গ্রন্থ আলোচনাঃ নির্বাসিতের আত্মকথা
বইটির খোঁজ পাই মুজতবা সাহেবের পঞ্চতন্ত্রে। এমন সুরসিক ও পণ্ডিত লেখক যে বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করছেন তা একবার চেখে দেখা আবশ্যক মনে হয়েছিল। করে ফেললাম। এবং আমার পাঠেন্দ্রিয় সার্থক। ১৯২১ সালে প্রকাশিত বইয়ে বেশির ভাগ জায়গায় পাওয়া যায় পরিমিত হাস্যবোধ আর কিছু জায়গায় আবেগের নির্মম পেষণ।
লেখক উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যে হাস্যরস তৈরিতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত তা বইটির প্রথম ক পাতাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর শুধু উপেনবাবুর লিখার স্রোতে গা ভাসিয়ে ভেসে চলা। মূলত ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের কাহিনী এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। ডাক্তারি শেষ না করে বি এ পাস করে শিক্ষকতার শুরুর পর বন্দে মাতরম পত্রিকার জের ধরে 'যুগান্তর' সমিতিতে যোগদান। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়কার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল অনুশীলন সমিতি আর এই যুগান্তর। সেই সংগঠনটির একজন সক্রিয় সদস্যের বয়ানে সেই সময়কার নানা বিষয় মূর্ত হয়ে উঠে উপভোগ্য স্বাদে।
বারীন্দ্র ঘোষকে ঘিরে যুগান্তর হয়ে উঠে ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মূল শিকড়। যদিও বেশিরভাগ সদস্যই নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কেবল বিপ্লব ঘটানোর মননে একজোট, তারপরো এদের বন্দুক-বোমার জোর না থাকলেও গলাবাজি দিয়ে তারা তা পুষিয়ে দিতে সক্ষম। উপেনবাবুর এই বই এইসব আদর্শবাদী তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে। যার প্রথম অংশ ক্ষুদিরাম বসুর ১৯০৮ সালের হামলার পর আলিপুর বোমা মামলা পর্যন্ত ১৯০৬ থেকে এবং দ্বিতীয় অংশ বার বছর আন্দামানে কারাবাস নিয়ে।
এই প্রথম অংশের রস-কৌতুকের বিস্তার একেবারে গলা অবধি।
মানিকতলায় এই নব্যবিপ্লবীদের আখড়া গড়ে উঠে। তাদের আদর্শকে একবাক্যে তিনি মেনে নিয়েছেন এই কথা দিয়েঃ
লেখক উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যে হাস্যরস তৈরিতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত তা বইটির প্রথম ক পাতাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর শুধু উপেনবাবুর লিখার স্রোতে গা ভাসিয়ে ভেসে চলা। মূলত ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের কাহিনী এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। ডাক্তারি শেষ না করে বি এ পাস করে শিক্ষকতার শুরুর পর বন্দে মাতরম পত্রিকার জের ধরে 'যুগান্তর' সমিতিতে যোগদান। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়কার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল অনুশীলন সমিতি আর এই যুগান্তর। সেই সংগঠনটির একজন সক্রিয় সদস্যের বয়ানে সেই সময়কার নানা বিষয় মূর্ত হয়ে উঠে উপভোগ্য স্বাদে।
 | |
|
বারীন্দ্র ঘোষকে ঘিরে যুগান্তর হয়ে উঠে ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মূল শিকড়। যদিও বেশিরভাগ সদস্যই নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কেবল বিপ্লব ঘটানোর মননে একজোট, তারপরো এদের বন্দুক-বোমার জোর না থাকলেও গলাবাজি দিয়ে তারা তা পুষিয়ে দিতে সক্ষম। উপেনবাবুর এই বই এইসব আদর্শবাদী তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে। যার প্রথম অংশ ক্ষুদিরাম বসুর ১৯০৮ সালের হামলার পর আলিপুর বোমা মামলা পর্যন্ত ১৯০৬ থেকে এবং দ্বিতীয় অংশ বার বছর আন্দামানে কারাবাস নিয়ে।
এই প্রথম অংশের রস-কৌতুকের বিস্তার একেবারে গলা অবধি।
মানিকতলায় এই নব্যবিপ্লবীদের আখড়া গড়ে উঠে। তাদের আদর্শকে একবাক্যে তিনি মেনে নিয়েছেন এই কথা দিয়েঃ
"We want absolute autonomy from British control"
তারা এখানে 'যুগান্তর' পত্রিকার কাজের পাশাপাশি নতুন সদস্য যোগাড়ের কাজ করে। আড্ডা দেয়। নতুন আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য সাধুর খোঁজ করে। একবার ভারতময় সাধুর খোঁজে বেরিয়ে পরে উপেন ও তাঁর দলবল। নর্মদার উৎপত্তিস্থলে তিনি উদাসী সাধকদের সাথে ছাই মেখে নেপাল ঘুরতে চলেন। এই অভিযানে এই সন্ন্যাসব্রতের কষ্টসাধন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে মুক্তি চান। বারীনের নতুন উদ্যমে দল সাজানোর ডাক পেয়ে "তল্পির মধ্যে লোটা কম্বল আর তল্পার মধ্যে একগাছা মোটা লাঠি" নিয়ে ছুটে আসেন কলকাতা। সাধুব্রতের আধ্যাত্মিকতার খোঁজের এখানেই সমাপ্তি।
১৯০৭ সালে উল্লাসকর দত্তের দলে যোগ দেয়াতে বোমা বানানোর তোরজোড় শুরু হয় এবং বাংলার লাটসাহেব লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে বোমা দিয়ে ঘায়েল করার ফন্দি আঁটে বিপ্লবীরা। কিন্তু অনভিজ্ঞতা তাদের কাল হল। তারা ডিনামাইট জোগাড় করে ট্রেইন উলটে দেয়ার চিন্তা করল। রেললাইনের নিচে ডিনামাইটের কার্ট্রিজ রেখে দেয়া হল। আর তাতে -
এর কিছুদিন পরেই ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল উল্লাসকরের বানানো বোমা দিয়ে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে পুলিশ মানিকতলায় হানা দিয়ে সকল সদস্যকে ধরে নিয়ে যায়। লেখকের ভাষ্যমতে তারা এতটাই অনভিজ্ঞ ছিল যে, ক্রমশ তাদের আঙ্গিনায় যে অপরিচিত লোকেদের আনাগোনা বাড়ছিল, তাতে তারা মোটেও গা করে নি। কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদ ছিল। যার ফলে সকল সদস্য এক অপরের পরিচিত ছিল। ইউরোপে-আয়ারল্যান্ডে যেমন নানা বিচাগ-নানা এলাকায় আলাদা পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত তা তারা করতে পারে নি। ফলে আলীপুর বোমা হামলার ঠিক দুদিনের মধ্যে তারা সবাই তাদের মানিকতলার ঘাঁটি থেকে পাকড়াও হয়। ধরা পরার কাহিনীটা লেখক এঁকেছেন নিপুণ হাস্যরসের তুলিতে। ভাগ্যের পরিহাসকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছেন।
ঘুমোতে যাবার সময় পাহারা রাখা হয়নি এটা যেমন ভুল তেমনি পালিয়ে না যেয়ে পুলিশের কথায় বিশ্বাস করে সঙ্গী সাথীদের কথা প্রকাশ করা আরো মারাত্মক ভুল। বারীন ঘোষ এ হামলার আশংকা করে অস্ত্র-বোমা মাটিতে পুঁতে ফেললেও নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে পারেননি। রাতের আঁধারে পুলিশের সাথে চোর পুলিশ খেলতে যেয়ে উপেন বাবু আশ্রয় নেন বারান্দার পাশে একটা ছোট স্টোররুমে। চটের পার্দার আড়ালে আরশোলা আর ইঁদুরের সাথী হয়ে ভোর সাতটা পর্যন্ত সেখানে কাটান। সেই সময় ইনস্পেক্টর সাহেবের খেয়ালের বসে রুমের কাছে আসেন। তখন উপেন বাবু পর্দার ওপারে দম বন্ধ করে আছেন পর্দানসীন বিবির মতো। লেখকের ভাষায়-
এরপর তাদের জেরা করে বের করার চেষ্টা চলে অন্যান্য বিদ্রোহীদের পরিচয়। যুবকগুলোর ভুলোপনার সুযোগ নিয়ে পুলিশ তাদের থেকে আদায় করে নেয় স্বীকারোক্তি। একজন সব বলে দিয়েছে বলে অন্যদের থেকে কাহিনী বের করার বহু পুরনো ছলের শিকার হন লেখকের বেরাদরেরা।
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্টেটমেন্ট নিয়ে সবাইকে পাঠানো হয় আলিপুর জেলে। সেখানে যেয়ে প্রথম জেলের স্বাদ পান উপেন বাবু। কারাগারে নরক গুলজার।
প্রথমদিকটাতে মানাতে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে এসবের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পরেন। লপসী(ফেনমাখানো ভাত) ছিল জাতীয় খাবার। তাই খেয়েই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন জেলের ভেতরেও টাকার শক্তি। রুপোর সিকির জোরে ভাতের স্তূপের নিচে কই মাছ ভাজা মেলে, রুটির ফাঁক থেকে বের হয় আলু পেঁয়াজের তরকারি। আবার প্রহরীর পাগড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে পান-চুরুট। ব্রিটিশদের মতে আদর্শ শাসনব্যবস্থার কাছাকাছি একটা ব্যবস্থায় তাদের অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হলেও এখানে ঘুষ আর অনিয়মের যে ব্যাপক বিস্তৃতি তা তিনি দেখিয়েছেন বারবার। আর শাসনব্যবস্থার আনুকূল্যলাভের আশায় স্বদেশীদের প্রতি ভারতীয়-বাঙ্গালিদের যে অতিরিক্ত অত্যাচার তাতেও ব্যথিত হয়েছেন উপেনবাবু।
অরবিন্দ ঘোষ এই সময়ে শ্রী অরবিন্দ হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর ভাবচেতনার জগতের পরিবর্তনের একাংশ আলিপুরের কারাবাস পর্বে দেখা যায়। আলিপুর বোমা মামলাতে তাঁর খালাস হবে এটা আগেই বলে দেন তিনি। এই মামলায় মুক্তির পর তিনি পন্ডিচেরি চলে যান। এরই মাঝে তাদের একজন, নরেন্দ্র গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়ে জেলারের হেফাজতে চলে গেলে তাকে মারতে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু একটি কান্ড করে ফেলে। নরেন্দ্র মারা পড়ে গুলির আঘাতে। সেইসাথে কানাইলালের হয় ফাঁসি।
এইসব ঘটনার মাঝেই তীব্র হুল্লোড়-মচ্ছব করে দিন কেটে যাচ্ছিল কিন্তু ১৯০৯ সালে রায় ঘোষিত হয়। উল্লেখ্য, বিপ্লবীদের টাকা-পয়সা ছিল না দেখে কোন উকিলই মামলা নিচ্ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন দেশবন্ধু সি আর দাশ। রায় আসে বেশিরভাগেরই যাবজ্জীবন কালাপানি। উপেন-সাথে উল্লাসকর, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, সুধীর, হৃষীকেশের দ্বীপান্তর সাজা হয়। হৃষীকেশ ছিলেন উপেনের পূর্বতন বন্ধু। তাঁর প্রসঙ্গে তিনি লেখেন-
কালাপানি অধ্যায় সময়ের হিসেবে বড় হলেও লেখক একটু তাড়াহুড়া করেছেন। তিনদিনের জাহাজ যাত্রায় নাবিকদের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করেন। কেননা তিনদানের আহার্য ছিল কেবল চিড়া। মুসলমানের মধ্যে সহানুভূতির সাথে যে ব্রাহ্মণের ধর্মাচার বিগড়ানোর অভিপ্রায় ছিল তা উপেন বাবুরা অগ্রাহ্য করেন। ধর্ম রক্ষা হয়েছিল কিনা তা না জানলেও তাদের পিতৃপ্রদত্ত প্রাণটা বেঁচেছিল।
কালাপানিতে যেয়ে নিতান্ত কঠিন সময়ের সম্মুখীন হন তারা। জেলারদের যথেচ্ছ অত্যাচার, শাস্তির প্রকার বিবেচনায় না এনে শ্রমের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ, কাজ আদায় করে নিতে নিষ্ঠুরতা - সবকিছু দেখে মানুষের জন্য স্বাভাবিক থাকা দুষ্কর। তার উপর রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে সরকারের নির্দেশ ছিল অন্যান্য আসামী থেকে যেন বেশি সুবিধা না দেয়া হয়। ফলে ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠে কারাবাস। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত শুরু হয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্পর্কে আত্মোপলব্ধি ও অনুশোচনা। কীভাবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও গল্প করার প্রবণতার কারণে নিজেদের উপর এই শাস্তির খড়গ নেমে এসেছে তা হাড়ে হাড়ে টের পান লেখক। বিপ্লবীদের স্বাধীন হওয়া নিয়ে দ্বিমত না থাকলেও স্বাধীন হওয়ার পর দেশচালনা নিয়ে বহুমত বিদ্যমান ছিল। আর নেতাদের লোভ নিয়ে খুব অল্প করে প্রকাশ করছেন উপেন বাবু এভাবে-
আবার তিনি টলস্টয়ের Resurrection এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন বিপ্লবীরা স্বভাবতই অহংকারী ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয় যার বলে তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে উদ্ধত হয়। তারা সাধারণত কল্পনাপ্রবণ ও একদেশদর্শী। বেশিরভাগই আবার নিউরোটিক। ফলে পাগল হয়ে যাবার প্রবণতা বেশি থাকে। এই দাবী করার পেছনে উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, তাঁর পিতামহী বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন ও অনেক বিপ্লবীদের বংশের মধ্যে এই রোগ পাওয়া যায়।
তাঁর লেখাতে পোর্ট ব্লেয়ারের কাঠামোগত বর্ণনা নেই বললেই চলে। তেতলা ভবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে রাজবন্দিদের এখানে পাঠানো হতো। বাহাদুর শাহের বংশধর ও অনুসারী হতে শুরু করে রাজ বিদ্রোহীদের এখানে লম্বা শাস্তির জন্য পাঠানো হতো। বেশিরভাগের জন্যই জীবিত ফিরে আসা সম্ভব হত না। আর মারা গেলে সাগরের বুকে ভাসিয়ে দেয়া হতো।
১৯০৭ সালে উল্লাসকর দত্তের দলে যোগ দেয়াতে বোমা বানানোর তোরজোড় শুরু হয় এবং বাংলার লাটসাহেব লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে বোমা দিয়ে ঘায়েল করার ফন্দি আঁটে বিপ্লবীরা। কিন্তু অনভিজ্ঞতা তাদের কাল হল। তারা ডিনামাইট জোগাড় করে ট্রেইন উলটে দেয়ার চিন্তা করল। রেললাইনের নিচে ডিনামাইটের কার্ট্রিজ রেখে দেয়া হল। আর তাতে -
উড়া ত দূরের কথা-ট্রেনখানা একটু হেলিলও না। শুধু কার্ট্রিজ ফাটার গোটা দুই ফট ফট আওয়াজ শূন্যে মিলিয়ে গেল, লাটসাহেবের একটু ঘুমের ব্যাঘাত পর্যন্ত ঘটিল না।
এর কিছুদিন পরেই ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল উল্লাসকরের বানানো বোমা দিয়ে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে পুলিশ মানিকতলায় হানা দিয়ে সকল সদস্যকে ধরে নিয়ে যায়। লেখকের ভাষ্যমতে তারা এতটাই অনভিজ্ঞ ছিল যে, ক্রমশ তাদের আঙ্গিনায় যে অপরিচিত লোকেদের আনাগোনা বাড়ছিল, তাতে তারা মোটেও গা করে নি। কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদ ছিল। যার ফলে সকল সদস্য এক অপরের পরিচিত ছিল। ইউরোপে-আয়ারল্যান্ডে যেমন নানা বিচাগ-নানা এলাকায় আলাদা পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত তা তারা করতে পারে নি। ফলে আলীপুর বোমা হামলার ঠিক দুদিনের মধ্যে তারা সবাই তাদের মানিকতলার ঘাঁটি থেকে পাকড়াও হয়। ধরা পরার কাহিনীটা লেখক এঁকেছেন নিপুণ হাস্যরসের তুলিতে। ভাগ্যের পরিহাসকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছেন।
ঘুমোতে যাবার সময় পাহারা রাখা হয়নি এটা যেমন ভুল তেমনি পালিয়ে না যেয়ে পুলিশের কথায় বিশ্বাস করে সঙ্গী সাথীদের কথা প্রকাশ করা আরো মারাত্মক ভুল। বারীন ঘোষ এ হামলার আশংকা করে অস্ত্র-বোমা মাটিতে পুঁতে ফেললেও নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে পারেননি। রাতের আঁধারে পুলিশের সাথে চোর পুলিশ খেলতে যেয়ে উপেন বাবু আশ্রয় নেন বারান্দার পাশে একটা ছোট স্টোররুমে। চটের পার্দার আড়ালে আরশোলা আর ইঁদুরের সাথী হয়ে ভোর সাতটা পর্যন্ত সেখানে কাটান। সেই সময় ইনস্পেক্টর সাহেবের খেয়ালের বসে রুমের কাছে আসেন। তখন উপেন বাবু পর্দার ওপারে দম বন্ধ করে আছেন পর্দানসীন বিবির মতো। লেখকের ভাষায়-
সাহেব সোজা আসিয়া আমার লজ্জানিবারণী পর্দাখানিকে একটানে সরাইয়া দিলেন। তারপরেই চারিচক্ষের মিলন-কি মধুর! কি স্নিগ্ধ! কি প্রেমময়!
এরপর তাদের জেরা করে বের করার চেষ্টা চলে অন্যান্য বিদ্রোহীদের পরিচয়। যুবকগুলোর ভুলোপনার সুযোগ নিয়ে পুলিশ তাদের থেকে আদায় করে নেয় স্বীকারোক্তি। একজন সব বলে দিয়েছে বলে অন্যদের থেকে কাহিনী বের করার বহু পুরনো ছলের শিকার হন লেখকের বেরাদরেরা।
পুলীস যে ঠিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বংশ-সদ্ভূত নয় এ কথাটা তখন আমাদের মাথায় ভালো করিয়া ঢুকে নাই।
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্টেটমেন্ট নিয়ে সবাইকে পাঠানো হয় আলিপুর জেলে। সেখানে যেয়ে প্রথম জেলের স্বাদ পান উপেন বাবু। কারাগারে নরক গুলজার।
প্রথমদিকটাতে মানাতে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে এসবের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পরেন। লপসী(ফেনমাখানো ভাত) ছিল জাতীয় খাবার। তাই খেয়েই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন জেলের ভেতরেও টাকার শক্তি। রুপোর সিকির জোরে ভাতের স্তূপের নিচে কই মাছ ভাজা মেলে, রুটির ফাঁক থেকে বের হয় আলু পেঁয়াজের তরকারি। আবার প্রহরীর পাগড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে পান-চুরুট। ব্রিটিশদের মতে আদর্শ শাসনব্যবস্থার কাছাকাছি একটা ব্যবস্থায় তাদের অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হলেও এখানে ঘুষ আর অনিয়মের যে ব্যাপক বিস্তৃতি তা তিনি দেখিয়েছেন বারবার। আর শাসনব্যবস্থার আনুকূল্যলাভের আশায় স্বদেশীদের প্রতি ভারতীয়-বাঙ্গালিদের যে অতিরিক্ত অত্যাচার তাতেও ব্যথিত হয়েছেন উপেনবাবু।
অরবিন্দ ঘোষ এই সময়ে শ্রী অরবিন্দ হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর ভাবচেতনার জগতের পরিবর্তনের একাংশ আলিপুরের কারাবাস পর্বে দেখা যায়। আলিপুর বোমা মামলাতে তাঁর খালাস হবে এটা আগেই বলে দেন তিনি। এই মামলায় মুক্তির পর তিনি পন্ডিচেরি চলে যান। এরই মাঝে তাদের একজন, নরেন্দ্র গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়ে জেলারের হেফাজতে চলে গেলে তাকে মারতে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু একটি কান্ড করে ফেলে। নরেন্দ্র মারা পড়ে গুলির আঘাতে। সেইসাথে কানাইলালের হয় ফাঁসি।
এইসব ঘটনার মাঝেই তীব্র হুল্লোড়-মচ্ছব করে দিন কেটে যাচ্ছিল কিন্তু ১৯০৯ সালে রায় ঘোষিত হয়। উল্লেখ্য, বিপ্লবীদের টাকা-পয়সা ছিল না দেখে কোন উকিলই মামলা নিচ্ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন দেশবন্ধু সি আর দাশ। রায় আসে বেশিরভাগেরই যাবজ্জীবন কালাপানি। উপেন-সাথে উল্লাসকর, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, সুধীর, হৃষীকেশের দ্বীপান্তর সাজা হয়। হৃষীকেশ ছিলেন উপেনের পূর্বতন বন্ধু। তাঁর প্রসঙ্গে তিনি লেখেন-
উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে - যে একসঙ্গে গিয়া দাঁড়ায় সেই বান্ধব।
কালাপানি অধ্যায় সময়ের হিসেবে বড় হলেও লেখক একটু তাড়াহুড়া করেছেন। তিনদিনের জাহাজ যাত্রায় নাবিকদের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করেন। কেননা তিনদানের আহার্য ছিল কেবল চিড়া। মুসলমানের মধ্যে সহানুভূতির সাথে যে ব্রাহ্মণের ধর্মাচার বিগড়ানোর অভিপ্রায় ছিল তা উপেন বাবুরা অগ্রাহ্য করেন। ধর্ম রক্ষা হয়েছিল কিনা তা না জানলেও তাদের পিতৃপ্রদত্ত প্রাণটা বেঁচেছিল।
কালাপানিতে যেয়ে নিতান্ত কঠিন সময়ের সম্মুখীন হন তারা। জেলারদের যথেচ্ছ অত্যাচার, শাস্তির প্রকার বিবেচনায় না এনে শ্রমের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ, কাজ আদায় করে নিতে নিষ্ঠুরতা - সবকিছু দেখে মানুষের জন্য স্বাভাবিক থাকা দুষ্কর। তার উপর রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে সরকারের নির্দেশ ছিল অন্যান্য আসামী থেকে যেন বেশি সুবিধা না দেয়া হয়। ফলে ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠে কারাবাস। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত শুরু হয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্পর্কে আত্মোপলব্ধি ও অনুশোচনা। কীভাবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও গল্প করার প্রবণতার কারণে নিজেদের উপর এই শাস্তির খড়গ নেমে এসেছে তা হাড়ে হাড়ে টের পান লেখক। বিপ্লবীদের স্বাধীন হওয়া নিয়ে দ্বিমত না থাকলেও স্বাধীন হওয়ার পর দেশচালনা নিয়ে বহুমত বিদ্যমান ছিল। আর নেতাদের লোভ নিয়ে খুব অল্প করে প্রকাশ করছেন উপেন বাবু এভাবে-
যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতা লোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য।
আবার তিনি টলস্টয়ের Resurrection এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন বিপ্লবীরা স্বভাবতই অহংকারী ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয় যার বলে তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে উদ্ধত হয়। তারা সাধারণত কল্পনাপ্রবণ ও একদেশদর্শী। বেশিরভাগই আবার নিউরোটিক। ফলে পাগল হয়ে যাবার প্রবণতা বেশি থাকে। এই দাবী করার পেছনে উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, তাঁর পিতামহী বায়ুরোগগ্রস্ত ছিলেন ও অনেক বিপ্লবীদের বংশের মধ্যে এই রোগ পাওয়া যায়।
তাঁর লেখাতে পোর্ট ব্লেয়ারের কাঠামোগত বর্ণনা নেই বললেই চলে। তেতলা ভবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে রাজবন্দিদের এখানে পাঠানো হতো। বাহাদুর শাহের বংশধর ও অনুসারী হতে শুরু করে রাজ বিদ্রোহীদের এখানে লম্বা শাস্তির জন্য পাঠানো হতো। বেশিরভাগের জন্যই জীবিত ফিরে আসা সম্ভব হত না। আর মারা গেলে সাগরের বুকে ভাসিয়ে দেয়া হতো।
উপেনবাবুর বর্ণনাতে কয়েদীদের কাজকর্মের বিবরণ মেলে। কয়েদীদের দিয়ে সেখানে নারিকেল ও সরিষার তেল তৈরির জন্য ঘানি টানানো হয়। মাথাপিছু দৈনিক ৩০ পাউন্ড। এছাড়া আরেকটি পরিশ্রমের কাজ নারকেলে ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরি করা। এই দুটো কাজের দায়িত্ব পড়ে সেইসব কয়েদির উপর যাদেরকে অতিরিক্ত শ্রমের জন্য নির্বাচিত করা হয়।
নারকেলের দড়ি বানানোর পদ্ধতির বর্ণনা দেন উপেন্দ্রবাবু। প্রথমে ছোবড়া কাঠের উপর ফেলে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে নরম করে নেয়া লাগে। এরপর উপরের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। তারপর পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে আবার পিটিয়ে নিতে হত যাতে শক্ত, লম্বা তার গুলো বাদে ভুসিগুলো ঝড়ে যায়। শেষে রোদে শুকিয়ে নিলেও দড়ি পাকানোর জন্য তার প্রস্তুত হয়ে যায়। একদিনেই হাতে ফোসকা ফেলে দেবার জন্য এ যথেষ্ট।
খাবারের নিদারুণ অবহেলার সাথে আছে পাঠান পাহারাদারদের অবিবেচক অত্যাচার। সাধারণ কয়েদীদের পাঁচ বছর কারাভোগের পর আয় রোজগারের নানা পদ্ধতি থাকলেও রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য সে রাস্তা ছিল বন্ধ। শারীরিক অত্যাচারের সাথে ছিল অকথ্য গালিগালাজ। যেগুলো হজম করতে গেলেও তীব্র মানসিক শক্তির প্রয়োজন বলে লেখকের মন্তব্য পাওয়া যায়।
ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করে ফাঁস টাঙ্গিয়ে। উল্লাসকর কারাবাসেই মানসিক ভারাসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেকে মুক্তির আশায় পাগল হবার ভানও করে।
আন্দামানে যে যত শক্ত তার কদর তত বেশি। প্রহরীদের মাঝেও, কয়েদীদের মধ্যেও। এই শক্ত-পোক্তগিরিতে রক্ষকরা যদি কঠোর উপায়ে কাজ হাসিল করতে পারতো তবেই কয়েদীরা বলতো-'শালা বড় মারদ হৈ'। আর নরম আচরণ নারীর স্বভাব প্রকাশ করার মতো। জীবনযুদ্ধের এ নির্মমতম শিক্ষা (!) চল্লিশ বছর পার করে উপেনবাবুর মাথায় ঢোকে।
গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন শুরুর আগেই উপেন বাবু আন্দামানে Passive Resistance এর নমুনা দেখেন নন্দগোপাল নামের এক বিপ্লবী থেকে। নির্ধারিত সময়ে তেল তৈরির কোটা পূরণ না করে নিজের সুবিধামতো খেয়ে-ঘুমিয়ে কাজ করে জেলারের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে সে। শাসাতে এলে নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধির দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্তে আদেশ অমান্য করে যায়। শুরু হয় এর মাঝেই ধর্মঘট-অনশন। পরিশ্রম কমানো, সহনশীল খাবারের ব্যবস্থা ও মিত্রদের সাথে মেলামেশা করার চাহিদা-এই তিন দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান তারা। এরই সাথে ১৯১৪ সাল থেকে শুরু হয় 'গাদার' বা 'গদর' পার্টির শিখ বিদ্রোহীদের কালাপানিতে আগমন। তাদের খাবারের বন্দোবস্ত নিয়ে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ রাজ কিছুটা শিথিল হতে শুরু করে আর জেলের বাইরে নানা কাজে বাঙ্গালি বিপ্লবীদেরকে নিযুক্ত করতে থাকে। তাছাড়া কুঠুরির নিদারুণ ব্যবস্থাপনা, রোগ-শোকের চরম বেড়ে যাওয়া আর তার সাথে কয়েদীদের জবর ধর্মঘট সব মিলিয়ে সরকার রফায় আসতে বাধ্য হয়। পোশাক পরিধানে রীতি-নীতি উঠে যায়। মাইনে আসা শুরু হয়। নিজ হাতে রান্নার বন্দোবস্ত হয়। এসময়ে লেখকের মতে জাঙ্গিয়া, টুপি, হাতাকাটা কুর্তা ছেড়ে কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্তা পড়তে পারাটাও নিদারুণ আনন্দের ছিল।
এ কারাবাসে আরেকটি উপলব্ধির কথা লেখক লিখেছেন জাত-বৈচিত্র্য নিয়ে। জেলে হিন্দু-মুসলিম-শিখ, মারাঠা-বাঙ্গালি-পাঞ্জাবি-পাঠান-মাদ্রাজি-গুজরাতিদের সম্মিলন ঘটে কিন্তু ঠিক ঐক্যবোধটা দেখা যায় না। লেখক ঠিক কাঠখোট্টা ব্রাহ্মণত্বের অনুসারী না হলেও জাত-পাতের এই ভেদাভেদ দেখে ব্যথিত হন। সকলেই বামুনের উপর এক হাত দেখে নিতে পারলে যেন খুশি হয়। তার উপর কারাবাসের দীর্ঘ যাতনা ও অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে মানুষ যে কিছু একটার উপর ভরসা করবে-সেটাই স্বাভাবিক। তাই নিতান্ত গোবেচারা ঢিলেঢালা হিন্দুরাও ফুটখানেক টিকি রেখে দিত আর মুসলিমরা গজাত পেল্লাই দাড়ি। দিন দিন ধর্মের ভক্তি বাড়তে থাকে। আর তার সাথে বাড়ে অন্য ধর্ম থেকে নিজের ধর্মে নিয়ে আসার তোরজোড় বা নিতান্ত ধর্মে অনাসক্তদের কড়া বাঁধনে বাঁধার প্রয়াস। আবার জাতিগতভাবে দেখা যায় আরেক বিশাল পার্থক্য। ভারতীয় জাতিসত্ত্বার আড়ালে বহু মতবাদের চর্চা হত। মারাঠি নেতারা বলত, "বঙ্কিমবাবু 'বন্দে মাতরম' এ 'সপ্তকোটি' কন্ঠের কথা বলেছেন, তিরিশ কোটির কথা বলেননি। বাঙ্গালি কবিরা বলত, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার'। তাই বাঙ্গালির জাতীয়তাবোধ অতি সংকীর্ণ।" পাঞ্জাবী বলে, "রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল। তাই তিনি বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী।" মারাঠীদের মতে, ভারত কখনো একীভূত হলে তার শাসনভার থাকা উচিত মারাঠাদের হাতে। তাদের ভাব থেকে প্রতিভাত হয়-
এহেন উগ্র জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব সেই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ছিল তা এখানে বুঝা যায়। লেখক নিজেও শেষ বয়সে হিন্দু মহাসভায় যুক্ত হন। এই সংঘটি মূলত ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের জবাবে হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এরকম বহুধা আদর্শে ভারতীয়দের বিভাজনে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু ব্রিটিশ সরকার।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি-ভারত ষড়যন্ত্রে শামিল হয়ে প্রবাসী শিখদের একাংশের ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারত হতে উঠানোর যে তৎপরতা শুরু হয় তার উল্লেখ ও প্রভাব দেখা যায় এই বইয়ে। মাদ্রাজে এমডেনের বোমা হামলা হলে কালাপানির বাসিন্দারা উচ্ছ্বসিত হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেকোন শক্তির সপক্ষে বিপ্লবীদের অবস্থান এখানে লক্ষনীয়। আবার যুদ্ধ হতে বিদ্রোহের কারণে যেসব সৈন্য এখানে আসতো তাদের মুখে নানা মনগড়া কাহিনী শুনে অভিভূত হত কয়েদীরা। এর মাধ্যমে তুর্কি বাহিনীর এনভার পাশার কিংবদন্তী হয়ে উঠে। কয়েদীরা গুজবে বিশ্বাস করতে থাকে যে, জার্মানরা এসে কালাপানি হতে তাদেরকে নিয়ে যাবে। আইরিশরা কালাপানির ব্যবস্থাপনাতে বেশি থাকাতে অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতির আচরণ করা হত সহমর্মিতার খাতিরে। এমন কথাও শোনা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলে ব্রিটিশ রাজ কালাপানির বন্দিদের মুক্তি দিয়ে দিবে। এরই মাঝে রাশিয়ার বিপ্লব শুরু হয়। দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর পেরিয়ে যায়। ১৯২০ সালে জেল কমিটি এসে অবস্থা দেখে যেয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করে। মুক্তির দেখা মেলে না। এমনকি যুদ্ধের পরে জেলার সরকার থেকে ছুটি চাইলে তা মিলে না। কারণ তিনি আইরিশ। অবশেষে সেই মুক্তি আসে। তারা ২৬ জন বের হয়ে আসে।
কলকাতায় খিদিরপুর ঘাটে আন্দামান ডকে এসে নামে বার বছরের কালাপানি ভোগা উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। জুতা পরার অভ্যাস হারিয়ে ফেলা, কলকাতার রাস্তা ভুলে যাওয়া, জাত-পাতের জন্য নিজের আত্মাভিমান ফেলে আসা নতুন উপেনবাবু। সংকল্প
ছিল সংসারধর্মে মনোযোগী হওয়া। কিন্তু লেখক পরবর্তী জীবনে আবারো 'অ্যানার্কি'তে যুক্ত হন।
মুজতবা সাহেব লিখেছেন,
এ বাক্যের মহিমা পড়ামাত্রই টের পাওয়া যায়। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মাঝেও লেখক যে সূক্ষ্ম বিষয়ে রসিকতা খুঁজে নিয়েছেন, শঙ্কার সময়ের বর্ণনাতে ঢেলে দিয়েছেন নিজের বৈঠকি ঢং। মুজতবা আলী সাহেবের সাথে এক্ষেত্রে ভয়ানক মিল। তিনি নিজেও তাঁর সাথে দেখা করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর ভাষ্যেঃ
নারকেলের দড়ি বানানোর পদ্ধতির বর্ণনা দেন উপেন্দ্রবাবু। প্রথমে ছোবড়া কাঠের উপর ফেলে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে নরম করে নেয়া লাগে। এরপর উপরের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। তারপর পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে আবার পিটিয়ে নিতে হত যাতে শক্ত, লম্বা তার গুলো বাদে ভুসিগুলো ঝড়ে যায়। শেষে রোদে শুকিয়ে নিলেও দড়ি পাকানোর জন্য তার প্রস্তুত হয়ে যায়। একদিনেই হাতে ফোসকা ফেলে দেবার জন্য এ যথেষ্ট।
 | |
|
 | |
|
খাবারের নিদারুণ অবহেলার সাথে আছে পাঠান পাহারাদারদের অবিবেচক অত্যাচার। সাধারণ কয়েদীদের পাঁচ বছর কারাভোগের পর আয় রোজগারের নানা পদ্ধতি থাকলেও রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য সে রাস্তা ছিল বন্ধ। শারীরিক অত্যাচারের সাথে ছিল অকথ্য গালিগালাজ। যেগুলো হজম করতে গেলেও তীব্র মানসিক শক্তির প্রয়োজন বলে লেখকের মন্তব্য পাওয়া যায়।
ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করে ফাঁস টাঙ্গিয়ে। উল্লাসকর কারাবাসেই মানসিক ভারাসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেকে মুক্তির আশায় পাগল হবার ভানও করে।
আন্দামানে যে যত শক্ত তার কদর তত বেশি। প্রহরীদের মাঝেও, কয়েদীদের মধ্যেও। এই শক্ত-পোক্তগিরিতে রক্ষকরা যদি কঠোর উপায়ে কাজ হাসিল করতে পারতো তবেই কয়েদীরা বলতো-'শালা বড় মারদ হৈ'। আর নরম আচরণ নারীর স্বভাব প্রকাশ করার মতো। জীবনযুদ্ধের এ নির্মমতম শিক্ষা (!) চল্লিশ বছর পার করে উপেনবাবুর মাথায় ঢোকে।
গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন শুরুর আগেই উপেন বাবু আন্দামানে Passive Resistance এর নমুনা দেখেন নন্দগোপাল নামের এক বিপ্লবী থেকে। নির্ধারিত সময়ে তেল তৈরির কোটা পূরণ না করে নিজের সুবিধামতো খেয়ে-ঘুমিয়ে কাজ করে জেলারের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে সে। শাসাতে এলে নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধির দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্তে আদেশ অমান্য করে যায়। শুরু হয় এর মাঝেই ধর্মঘট-অনশন। পরিশ্রম কমানো, সহনশীল খাবারের ব্যবস্থা ও মিত্রদের সাথে মেলামেশা করার চাহিদা-এই তিন দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান তারা। এরই সাথে ১৯১৪ সাল থেকে শুরু হয় 'গাদার' বা 'গদর' পার্টির শিখ বিদ্রোহীদের কালাপানিতে আগমন। তাদের খাবারের বন্দোবস্ত নিয়ে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ রাজ কিছুটা শিথিল হতে শুরু করে আর জেলের বাইরে নানা কাজে বাঙ্গালি বিপ্লবীদেরকে নিযুক্ত করতে থাকে। তাছাড়া কুঠুরির নিদারুণ ব্যবস্থাপনা, রোগ-শোকের চরম বেড়ে যাওয়া আর তার সাথে কয়েদীদের জবর ধর্মঘট সব মিলিয়ে সরকার রফায় আসতে বাধ্য হয়। পোশাক পরিধানে রীতি-নীতি উঠে যায়। মাইনে আসা শুরু হয়। নিজ হাতে রান্নার বন্দোবস্ত হয়। এসময়ে লেখকের মতে জাঙ্গিয়া, টুপি, হাতাকাটা কুর্তা ছেড়ে কাপড় ও হাতাওয়ালা কুর্তা পড়তে পারাটাও নিদারুণ আনন্দের ছিল।
এ কারাবাসে আরেকটি উপলব্ধির কথা লেখক লিখেছেন জাত-বৈচিত্র্য নিয়ে। জেলে হিন্দু-মুসলিম-শিখ, মারাঠা-বাঙ্গালি-পাঞ্জাবি-পাঠান-মাদ্রাজি-গুজরাতিদের সম্মিলন ঘটে কিন্তু ঠিক ঐক্যবোধটা দেখা যায় না। লেখক ঠিক কাঠখোট্টা ব্রাহ্মণত্বের অনুসারী না হলেও জাত-পাতের এই ভেদাভেদ দেখে ব্যথিত হন। সকলেই বামুনের উপর এক হাত দেখে নিতে পারলে যেন খুশি হয়। তার উপর কারাবাসের দীর্ঘ যাতনা ও অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে মানুষ যে কিছু একটার উপর ভরসা করবে-সেটাই স্বাভাবিক। তাই নিতান্ত গোবেচারা ঢিলেঢালা হিন্দুরাও ফুটখানেক টিকি রেখে দিত আর মুসলিমরা গজাত পেল্লাই দাড়ি। দিন দিন ধর্মের ভক্তি বাড়তে থাকে। আর তার সাথে বাড়ে অন্য ধর্ম থেকে নিজের ধর্মে নিয়ে আসার তোরজোড় বা নিতান্ত ধর্মে অনাসক্তদের কড়া বাঁধনে বাঁধার প্রয়াস। আবার জাতিগতভাবে দেখা যায় আরেক বিশাল পার্থক্য। ভারতীয় জাতিসত্ত্বার আড়ালে বহু মতবাদের চর্চা হত। মারাঠি নেতারা বলত, "বঙ্কিমবাবু 'বন্দে মাতরম' এ 'সপ্তকোটি' কন্ঠের কথা বলেছেন, তিরিশ কোটির কথা বলেননি। বাঙ্গালি কবিরা বলত, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার'। তাই বাঙ্গালির জাতীয়তাবোধ অতি সংকীর্ণ।" পাঞ্জাবী বলে, "রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল। তাই তিনি বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী।" মারাঠীদের মতে, ভারত কখনো একীভূত হলে তার শাসনভার থাকা উচিত মারাঠাদের হাতে। তাদের ভাব থেকে প্রতিভাত হয়-
হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙ্গালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্ব্বল ও ভীরু-একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ।
এহেন উগ্র জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব সেই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ছিল তা এখানে বুঝা যায়। লেখক নিজেও শেষ বয়সে হিন্দু মহাসভায় যুক্ত হন। এই সংঘটি মূলত ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের জবাবে হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এরকম বহুধা আদর্শে ভারতীয়দের বিভাজনে অনেকাংশে দায়ী কিন্তু ব্রিটিশ সরকার।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি-ভারত ষড়যন্ত্রে শামিল হয়ে প্রবাসী শিখদের একাংশের ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারত হতে উঠানোর যে তৎপরতা শুরু হয় তার উল্লেখ ও প্রভাব দেখা যায় এই বইয়ে। মাদ্রাজে এমডেনের বোমা হামলা হলে কালাপানির বাসিন্দারা উচ্ছ্বসিত হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেকোন শক্তির সপক্ষে বিপ্লবীদের অবস্থান এখানে লক্ষনীয়। আবার যুদ্ধ হতে বিদ্রোহের কারণে যেসব সৈন্য এখানে আসতো তাদের মুখে নানা মনগড়া কাহিনী শুনে অভিভূত হত কয়েদীরা। এর মাধ্যমে তুর্কি বাহিনীর এনভার পাশার কিংবদন্তী হয়ে উঠে। কয়েদীরা গুজবে বিশ্বাস করতে থাকে যে, জার্মানরা এসে কালাপানি হতে তাদেরকে নিয়ে যাবে। আইরিশরা কালাপানির ব্যবস্থাপনাতে বেশি থাকাতে অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতির আচরণ করা হত সহমর্মিতার খাতিরে। এমন কথাও শোনা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলে ব্রিটিশ রাজ কালাপানির বন্দিদের মুক্তি দিয়ে দিবে। এরই মাঝে রাশিয়ার বিপ্লব শুরু হয়। দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর পেরিয়ে যায়। ১৯২০ সালে জেল কমিটি এসে অবস্থা দেখে যেয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করে। মুক্তির দেখা মেলে না। এমনকি যুদ্ধের পরে জেলার সরকার থেকে ছুটি চাইলে তা মিলে না। কারণ তিনি আইরিশ। অবশেষে সেই মুক্তি আসে। তারা ২৬ জন বের হয়ে আসে।
কলকাতায় খিদিরপুর ঘাটে আন্দামান ডকে এসে নামে বার বছরের কালাপানি ভোগা উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। জুতা পরার অভ্যাস হারিয়ে ফেলা, কলকাতার রাস্তা ভুলে যাওয়া, জাত-পাতের জন্য নিজের আত্মাভিমান ফেলে আসা নতুন উপেনবাবু। সংকল্প
ছিল সংসারধর্মে মনোযোগী হওয়া। কিন্তু লেখক পরবর্তী জীবনে আবারো 'অ্যানার্কি'তে যুক্ত হন।
মুজতবা সাহেব লিখেছেন,
"সকল বাঙ্গালির অবশ্য পাঠ্য"
এ বাক্যের মহিমা পড়ামাত্রই টের পাওয়া যায়। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মাঝেও লেখক যে সূক্ষ্ম বিষয়ে রসিকতা খুঁজে নিয়েছেন, শঙ্কার সময়ের বর্ণনাতে ঢেলে দিয়েছেন নিজের বৈঠকি ঢং। মুজতবা আলী সাহেবের সাথে এক্ষেত্রে ভয়ানক মিল। তিনি নিজেও তাঁর সাথে দেখা করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর ভাষ্যেঃ
"আমার ইচ্ছে ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরকযন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তাঁর কতখানি সত্যই তাঁর চরিত্রবলের দরুন এই বিশেষরূপ নিল আর কতটা নিছক সাহিত্য-শৈলী মাত্র"
তবে তিনি লিখে গেছেন,
"আমার মতো একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তাঁর থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলাম যে, তাঁর ভিতর মানুষকে টেনে আনবার কোন আকর্ষণীয় ক্ষমতা ছিল, যার জন্য বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হয়েছিল।"
নিজের পরিবারের কথা খুব সামলে এড়িয়ে গেছেন লেখক। কেবল এসেছে দেড় বছরের পুত্রের কথা যখন তিনি কালাপানি রওনা হন আর যখন ফিরে আসেন তখন কিশোর ছেলেকে দেখেন।
এ বইয়ের মাহাত্ম্য সেই সময়কার বর্ণনাজ্ঞাপনে যখন বাংলা স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল, রাজযন্ত্রের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ দানা বাঁধছে। এরই মাঝে কিভাবে কতিপয় বাঙ্গালি যুবক গান্ধীজীর অহিংসা প্রতিবাদের আগে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয় আনাড়ির মতো আর তার ফলস্বরূপ একযুগ দ্বীপান্তরে কারাবরন করে আসে - সেই গল্পই রসিয়ে, মজিয়ে নিবেদন করেছেন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিমশাই।
গদ্যের তরলতায় মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। উল্লেখ্য, এটাই লেখকের প্রথম প্রকাশনা। কালাপানির বর্ণনাতে কিছুটা ঝুলে গেলেও এক বসায় শেষ না করে উঠা প্রায় অসম্ভব। সকল সুরসিক পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। আবার বাঙ্গালি বিপ্লববাদের প্রথমদিককার কর্মকান্ডের ছোটখাটো দলিল। প্রামাণ্য না হলেও অনেক ধরণের অনুভূতির সন্নিবেশনে এটি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত গাঁথা। একই সাথে কৌতুকরস, বেদনারস, দর্শনরস, আত্মোপলব্ধিরস - এত সুন্দর করে ছোট্ট আকারে প্রকাশ করা খুব কম বইয়ে মিলবে। এত বিদ্রোহ-আন্দোলন-ধর্মঘটের পর শেষ পাতায় যেয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষা। এতেই পুরো লেখার সার্থকতাটা মূর্ত হয়ে উঠে।
গদ্যের তরলতায় মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। উল্লেখ্য, এটাই লেখকের প্রথম প্রকাশনা। কালাপানির বর্ণনাতে কিছুটা ঝুলে গেলেও এক বসায় শেষ না করে উঠা প্রায় অসম্ভব। সকল সুরসিক পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। আবার বাঙ্গালি বিপ্লববাদের প্রথমদিককার কর্মকান্ডের ছোটখাটো দলিল। প্রামাণ্য না হলেও অনেক ধরণের অনুভূতির সন্নিবেশনে এটি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত গাঁথা। একই সাথে কৌতুকরস, বেদনারস, দর্শনরস, আত্মোপলব্ধিরস - এত সুন্দর করে ছোট্ট আকারে প্রকাশ করা খুব কম বইয়ে মিলবে। এত বিদ্রোহ-আন্দোলন-ধর্মঘটের পর শেষ পাতায় যেয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষা। এতেই পুরো লেখার সার্থকতাটা মূর্ত হয়ে উঠে।
 |
| লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [উৎসঃ abasar.net ] |

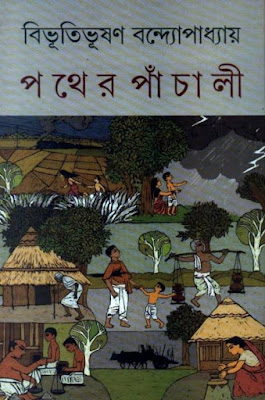
Comments
Post a Comment