বৌদ্ধ মতবাদ
বুদ্ধ কথাটার অর্থ হলো যিনি জেগে উঠেছেন, যিনি আলোকদীপ্ত হয়েছেন। মিলেনিয়াল ভাষায় WOKE এর মতো। কিন্তু ঠিক হালের হকিকত নিয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল - সেই অর্থে না। এই বুদ্ধত্বের বিচরণ আরো ব্যাপক জায়গা জুড়ে।
সেপিয়েন্স বইয়ের কথা দিয়েই শুরু করতে হয়,
"It all started with the food surplus"
খাদ্য উৎপাদনের আয়াস চলে যাওয়াতে মানুষজন গড়ে তুলতে থাকে বড় বড় নগর, বসতি। দজলা-ফোরাত-সিন্ধু-গঙ্গা-হুয়াংহো-নীলের দুধারের উর্বর মাটিতে বিশেষত শুরু হয় সভ্যতার আয়োজন। ভারতবর্ষে তখন দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য বলেই অধিকাংশ গবেষকের ধারণা। খাবারের চিন্তা ঘুচে গেলে দর্শন কপচানোর সময় পাওয়া যায়। কথাটা মিথ্যা না।
 |
| Gautam [Source: The Sentinel] |
বুদ্ধাগমনের পূর্ববর্তী ভারতঃ
ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের (১৮০০-১৭০০ বিসিই*) পর যে আন্তঃগোষ্ঠী কোন্দলের সূত্রপাত হয় তার সাথে লৌহ যুগের শুরু হওয়াতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর্যরা বৈদিক ভাষায় (সংস্কৃত) লিখত ও কথা বলতো। তাই সেই থেকে বৈদিক যুগের শুরু। হিন্দু ধর্মের নামটাও ঠিক না, সেই হিসেবে। সিন্ধু>হিন্দু (পারস্যদের দেয়া নাম)। বরং এই ধর্মের নাম বৈদিক হওয়াই যুক্তিযুক্ত।
বৈদিক যুগে জাতভেদের চরম কড়াকড়ি ছিল। এর শিখরে অবস্থান করতো ব্রাহ্মণরা। তবে সেই সময়ে ব্রাহ্মণ কেবল জন্মানুসারে হতো না। দ্রাবিড় (অনার্য) জাতির মাঝেও যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতো ও মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করতো তাঁদেরকে ব্রাহ্মণ হিসেবে গণ্য করা হতো*। মূল আর্যরা তো আছেই। শিক্ষার অধিকার ও যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা কেবল এই গোষ্ঠী কুক্ষিগত করে রাখাতে শুরু হয় প্রচন্ড ক্ষোভ। নিম্নবর্গের মানুষের সংখ্যাও বেশি ছিল। অসন্তোষ বাড়ে। সাথে প্রচুর ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত জনপদ থাকায় মারামারি-হানাহানি-যুদ্ধ লেগেই থাকতো। বেদ-উপনিষদের বাণী আপ্তবাক্য হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণরাও আর নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার-গবেষণাতে জীবনীশক্তি ব্যয় করা থেকে বিরত হয় (৯০০-৮০০ বিসিই*)।
 |
| ১৬ মহাজনপদ (500 BCE) [Source: India the Destiny] |
এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশাল ব্যবধান দেখা দেয়। রাজ্য শাসন ও যুদ্ধে যেতো ক্ষত্রিয়। ধর্ম-কর্ম করতো ব্রাহ্মণ। ব্যবসা করতো বৈশ্য। আর ব্যাগার খাটতো শূদ্র ও অচ্ছুৎরা। আবার, সেই সময়ে লোহার ব্যাপক ব্যবহারে কৃষির উন্নতি হওয়ায় ব্যবসা-বানিজ্যেও আসে বিপুল সাফল্য। আলাদাভাবে ক্ষমতাশালী বণিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ফলে সমাজের তলানিতে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্ররাই পড়ে থাকে। ইতোমধ্যে আর্যদের দ্বারা এক বিশাল অনার্য জনগোষ্ঠী সিন্ধু-গঙ্গার অববাহিকা থেকে পূর্বে ও দক্ষিণে নির্বাসিত হয়। যারা ছিল তারা উচ্চ-বর্ণের বৈদিক জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত ছিল।
উল্লেখ্য, এই সামাজিক অস্থিরতা কেবল ভারতেই ছিল তা নয়। চীন, মধ্যপ্রাচ্য (আরব-লেভান্ট-মেসোপটেমিয়া), পারস্যসহ সকল সভ্যতার আঁতুড়ঘরে দেখা যাচ্ছিল। সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব, যুদ্ধবিগ্রহের পেছনে অতিরিক্ত খরচ, ক্ষমতার প্রচন্ড এককেন্দ্রিকতা, সম্পদের বিষম বন্টন। এই বিষয়গুলো প্রকট হওয়ার সাথে সাথে কনফুসিয়ান, লাউৎসু (চীন), জরাথ্রুস্ট (পারস্য), ইহুদি নবী (মধ্যপ্রাচ্য)দের মতো মহৎ সমাজ সংস্কারকরা আবির্ভূত হন। ভারতে দেখা দেন মহাবীর ও গৌতম। সকলেই একটি বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে নৈতিকতা ও সমাজের সংস্কার দরকার। এদের সকলের মাঝে গৌতমের শিক্ষা সবচেয়ে সফল কেননা তাঁর প্রচারিত উপদেশাবলি যে ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল তা আজো কোটি কোটি মানুষ মেনে চলছে। আর শান্তির বাহকরূপে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মানা হচ্ছে।
বৈদিক যুগের অন্যান্য সন্ন্যাসী গোষ্ঠীঃ
সন্ন্যাসের মাধ্যমে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা গৌতমই প্রথম প্রচলন করে, তা না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের সাথে বৈষম্য বেড়ে যাওয়াতে বেশ কিছু মানুষ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে দূরে চলে গিয়ে বনে বা শহরের বাইরে মাঠে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধ্যানে মগ্ন হতে থাকে। এই চর্চা বেশ কয়েকশ বছর ধরেই চলছিল। বৈদিক ধর্মেও এই প্রথা ছিল। পাশাপাশি আরো কিছু ধর্মগুরু তাঁদের স্বতন্ত্র দর্শন নিয়ে আলাদা সংঘ গড়ে তুলেন। সেসবের প্রভাব সেই যুগে মোটেও কম ছিল না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবাই মোটামুটি একদিক থেকে একই পথের পথিক ছিলেন-বৈদিক গ্রন্থের অসাড়তাতে বিশ্বাসী হয়ে মনের প্রশান্তি অর্জনের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন। সেইসব দলগুলোর মধ্যে বড় ও প্রভাবশালী ছিল বলা যায় নিচের দলগুলোকে।
অজীবকঃ- নিয়তিবাদী নাস্তিক। এই নামটি এসেছে 'অজীব' বা জড় থেকে। গৌতমের সমসাময়িক এদের উত্থান এবং বৈদিক বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে বুদ্ধবাদের পরই এদের স্থান ছিল। তাঁদের মতে, জগতের সবকিছু ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই কর্ম নিষ্প্রয়োজন (অক্রিয়া)। কেননা যে কর্মই করা হোক না কেন, নিয়তি বদলানো সম্ভব না। আবার তাঁরা নৈতিক কার্যকারণকে নাকচ করে দেয়। মানে কোন কাজের জন্য কোন কারণ দরকার পড়ে না বা এর থেকে কোন ফলাফল আসে না। কারণ, সবকিছুই তো ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
তাঁদের মতে, আত্মার স্থানান্তর ঘটে এবং এই চক্রের শেষ স্তর হলো অজীবক সন্ন্যাসী। তবে এর জন্য সময় লাগে লাখ লাখ বছর। কারণ প্রতিটি আত্মা যতগুলো জীবন ধারণ সম্ভব সগুলো পার হয়ে যায়। খুব সম্ভবত, এই অবান্তর বড় সংখ্যার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে আল বিরুনীর ভারততত্ত্ব বইয়ে। তাঁদের মতে জগৎ সংসার ৭টি উপাদান নিয়ে গঠিত- মাটি, পানি, বায়ু, তাপ, সুখ, দুঃখ, আত্মা (বা জীবন/'জীব')।
অজীবক ধর্মমত হাজার বছরের উপর ভারতে বিস্তৃত ছিল। ভারতের দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্বাংশে এদের বিচরণ বেশি ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা।
লোকায়ত বা চার্বাকঃ- বস্তুবাদী বা জড়বাদী নাস্তিক। প্রকৃতিবাদ এই দর্শনের মূলমন্ত্র। অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবেই এই চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। চার্বাক দর্শন এখানে আলোচ্য সকল দর্শনের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। বেদ-উপনিষদ, মহাভারতেও লোকায়তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, সকলের যা খুশি তা করার অধিকার আছে। কোন কিছুই ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলো যাবতীয় সুখ-শান্তির উদ্দেশ্য। ফলে জীবনে পার্থিব সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই দর্শনকে যদৃচ্ছাবাদও বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কাম বা যৌনতৃপ্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলে মানা হয় এই দর্শনমতে। যেহেতু মৃত্যুর পর কোন জগৎ নেই তাই যত ভোগ-বিলাস, আনন্দ তা এই জগতে করে নেয়াই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। আর সেই হিসেবে একেকজন মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশার চেয়ে সুখের পরিমাণ অনেক বেশি। আবার চার্বাকপন্থিরা নৈতিক কার্যকারণকে (সবকিছু ঘটা বা হওয়ার পেছনে কোন না কোন কারণ আছে) অস্বীকার করে অজীবকদের মতই কিন্তু অন্য কারণে। তাঁদের মতে, সবকিছুতে যেহেতু যা খুশি তাই করার ইচ্ছা আছে তাই কোন ঘটনা বা কাজের জন্য কোন কারণ বা উদ্দেশ্য থাকার দরকার নেই। তাঁদের মতে, বিশ্ব জগৎ চারটি উপাদান নিয়ে গঠিতঃ- মাটি, পানি, বায়ু ও তাপ/আগুন।
এই চিন্তাধারা বর্তমান জগতেও নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। এই জীবনটাকে পুরোপুরিভাবে উপভোগ করে নেয়ার দর্শনের যে নতুন যুগ শুরু হচ্ছে তার মূল কিন্তু এই লোকায়ত চিন্তাধারায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে তোড়জোড়, কোন বিষয়ে সমালোচনা গ্রাহ্য না করা কেননা সবারই যা খুশি তাই করার অধিকার আছে, সবকিছু মিলিয়ে এক জীবনের নেশায় সব নৈতিক-মানসিক বিষয়গুলাকে গিট্টু পাকায় ফেলা - এসব নব্যচার্বাকবাদ নয় তো কি?
সংশয়বাদীঃ- এই মতবাদধারীরা বিশ্বাস করতেন, কোন মতবাদ বা কোন বিশ্বাস নিয়েই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না। সব যুক্তি-তর্ক বেকার খাটনি। তাই তাঁরা সাধারণত বিতর্ক এড়িয়ে চলত বলে সেই সময়ের বইগুলোতে বলা হয়েছে। এই মতবাদের খুব বেশি প্রসার দেখা যায় নি। যদিও এই দর্শন এখনো কিন্তু টিকে আছে। শুধু প্রচার-প্রসার নেই। কেননা বিতর্কের খাতিরে গলা ফুলাতেই তাঁরা আগ্রহী নয়। কারণ তাঁরা এটাতেই নিশ্চিত হতে পারে না যে কোনটা আসলে ঠিক বা কোনটার দিকে যুক্তি ভারি। দোটানায় থাকার কারণে এ চিন্তাধারার স্ফুরণ সেভাবে হতে পারে নি।
জৈনঃ- কার্যকারণে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক আরেকটি দল হল জৈন। তাঁদের ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকলেও স্বর্গীয় সত্তাতে তাঁদের বিশ্বাস আছে। এরা বিখ্যাত এবং এখনো টিকে আছে। তারা বৌদ্ধদের মতো কার্যকারণে বিশ্বাসী। যদিও ধারণা করা হয়, এই গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে অজীবক দর্শন থেকে মহাবীর আলাদা হয়ে আসার পর। তারপরো তাঁদের মাঝে বুদ্ধসুলভ কিছু দর্শন বিদ্যমান। তাঁরা কর্মফলে বিশ্বাসী। তাঁরা প্রচণ্ড পরিমাণে নিরামিষাশী। সত্যিকার অর্থে তাঁরা বুদ্ধদের থেকেও বেশি কঠোর এই দিক দিয়ে। তাঁদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নিজের উপর অত্যাচার। জন্মের যে আবর্তে মানুষ ঘুরপাক খায় সেখানে কোন জন্মে করা খারাপ কর্মের ফল এই জীবনে পুষিয়ে দিতে হলে চরম মাত্রায় নিজের উপর অত্যাচার চালাতে হবে। তবেই মিলবে মুক্তি। টানা উপবাস বা খুব কম আহার (প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করে শেষ জীবনে কঠোর উপবাসে মৃত্যুবরণ করেন), সুতীব্র সন্ন্যাসব্রত, স্থাবর সকল সম্পত্তির বিসর্জন - এগুলো তাঁদের আচারের মধ্যে পড়ে। তাঁদের দর্শনের একটি বড় দিক হল - কোন জীবের তিলমাত্র ক্ষতি না করা। তাঁদের কাজকর্মের বিবরণে মনে হতেই পারে তারা বুঝি চরমপন্থি সন্ন্যাসী। কিন্তু আসলে মোটেও তা নয়। বরং তাঁরা চরমপন্থার বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ছিল। তাঁদের দুটি প্রধান শাখা আছে যারা মূলত সত্য সন্ধানের জন্য সন্ন্যাস ব্রত কীভাবে পালন করা উচিৎ, নারীদের মোক্ষলাভের গ্রহণযোগ্যতা, মন্দির ও প্রতিমার গঠন-সুরত এবং পালনীয় তীর্থঙ্কর ও গ্রন্থের ভাগে বিভক্ত। দিগম্বর (উলঙ্গ অবস্থায় সন্ন্যাস) ও শ্বেতাম্বর (সাদা পোশাকে সন্ন্যাস)। বৌদ্ধ মতের মত জৈন ধর্মে যারা মোক্ষ লাভ করে তাঁদেরকে আরিহৎ বলা হয়। আর যুগে যুগে জৈনদের পথ দেখাতে আবির্ভূত হন তীর্থঙ্কর। যেই ধারার প্রথম ছিলেন ঋষভ। তেইশতম ছিলেন পরশ্ব, যার অস্তিত্বের প্রমাণ ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে (চিত্র, ভাস্কর্য, পুস্তক) মেলে। আর সর্বশেষ ছিলেন মহাবীর। পর্যুষণ/দশ লক্ষণ তাঁদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এ সময়ে তাঁরা উপবাসসহ নানা আচার পালন করে পুণ্য কামিয়ে নিতে ব্রতী হয়। দেরাসর বা বসডিতে (জৈন মন্দির) সেসময় জমায়েত হয় ধর্মপ্রাণ জৈনদের। তাঁদের মূল পাঁচটি ব্রত হলঃ
১। অহিংসা
২। সত্য
৩। অস্ত্যেয় বা অচৌর্য (চুরি না করা)
৪। ব্রহ্মচর্য (কুমারব্রত)
৫। অপরিগ্রহ (সম্পদ ধারণ না করা)
এ তো গেলো বুদ্ধের আবির্ভাবের পেছনে সামাজিক প্রভাব ও কিঞ্চিৎ ইতিহাস। বুদ্ধের দর্শনের আলোচনার আগে তাঁর জীবন নিয়ে কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এটি নিয়ে বিশদ বই-পুস্তক, উইকিপাতা আছে। আমি দর্শনের আলোচনার জন্য জরুরি বিষয়েই আলোকপাত করবো বেশি।
বুদ্ধাগমনঃ
শাক্যগোষ্ঠীর হিমালয়ের কাছের এক রাজ্যের রাজা শুদ্ধোধনের ছেলে সিদ্ধার্থ (সর্বার্থসিদ্ধ-এর সংক্ষেপিত রূপ)। তাঁর জন্মকালেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে, এই ছেলে জগতের ভোল পাল্টে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তাঁকে দিয়ে রাজ্যের হাল ধরাতে চাইলে তাঁকে সর্বদা চারটি দৃশ্য হতে দূরে রাখতে হবে-
১) বার্ধক্য,
২) রোগ,
৩) মৃত্যু, এবং
৪) সন্ন্যাস।
 |
| Buddha Seeing Four Sights (Clockwise from top: Sickness, Death, Asceticism, Oldness) [Source: Gauthama Buddha Blogspot] |
এই চারটি বাস্তবতা হতে দূরে রেখে যাবতীয় পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত রাখতে পারলে গৌতম একসময় রাজ্যভার গ্রহণ করবে ও দিগ্বিজয়ী রাজা হয়ে উঠবে। রাজা শুদ্ধোদন তাঁর সাধ্যমতো সকল ব্যবস্থা পুত্রের জন্য করেছিলেন। ২৯ বছর সিদ্ধার্থ এর মাঝে ডুবে ছিলেন। তাঁর তিন ঋতুর জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল। ভোজন-কাম-শারীরিক ক্রীড়াসহ যাবতীয় বিলাসের আয়োজন তাঁর জন্য ছিল। কিন্তু একদিন তাঁর সামনে বাস্তবতা চলে আসে। তিনি ধীরে ধীরে চারটি দৃশ্যের সবকটির দেখে ফেলেন এবং এর পরিচয় পেয়ে যান। ইতোমধ্যে তিনি বিয়ে করেছিলেন ও রাহুল নামের সন্তানও ছিল তাঁর।
এখানে একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য যে, গৌতম গৃহত্যাগের আগ পর্যন্ত পুরোটা সময় জুড়েই রণকৌশল, রাজনীতি তথা রাজ্যচালনার রীতিসহ বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এবং শুদ্ধোধন এর জন্য চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখেন নি সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
তাঁর জীবনকাল ৫৬৬ খ্রি.পূ. থেকে ৪৫৬ খ্রি.পূ. ধরা হয়।* গৃহত্যাগ ৫৩৭ খ্রি.পূ. তে।*
গৃহত্যাগ ও নির্বাণঃ
এরপর কোন এক রাতে গৃহত্যাগী জ্যোৎস্নার আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি ঘর ছাড়েন। সন্ন্যাসব্রতের শিক্ষা নেন দুই গুরু থেকে। কিন্তু সন্তুষ্টি আসে না তাঁর। নিজের উপর অত্যাচার করে সন্ন্যাসব্রতের ধারণার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠেন (জৈন মতবাদের অন্যতম প্রধান কথা এটি)। তাঁর সমসাময়িক জৈন, অজীবক (ভাগ্যবাদ, তথা নিষ্কর্মবাদ), চার্বাক (নিরীশ্বরবাদ, প্রমাণসর্বস্ব), সংশয়বাদী - মতবাদগুলো তাঁর মতে সত্যপথের সন্ধান দিতে পারে না। তিনি কিছু ধারণার শুরুর দিককার শিক্ষা পেয়ে যান দুই গুরু থেক।
ঘর ছেড়ে দেয়ার পর পরই তাঁর সাথে দেখা হয় আরাদা কালামের। এই সাধু পুরুষ গৌতমকে কৌমার্যের শিক্ষা দেন। আর সেই সাথে আরাদার কাছ থেকেই গৌতমের শূন্যতা বা অস্তিত্বের না থাকার ধারণা জন্মে। এই শূন্যতার ধারণা আবার একেবারে অস্তিত্বহীনতার কথা। 'আমি নাই', 'তুমি নাই', 'কিছু নাই' রকমের কথাবার্তা। আরাদার কাছে তিনি খুব শীঘ্রই এই পাঠ চুকিয়ে নেন। শিক্ষক এতে অভিভূত হয়ে তাঁর দলের অধিপতির পদে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু গৌতম এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এই তীব্র অস্তিত্বহীনতার বুলি তাঁকে মন থেকে সায় দেয় না। তার উপর এই শিক্ষা গৌতমের কাছে কিছুটা সংকীর্ণ চিত্তের মনে হয়। তারপরও এই শিক্ষা তাঁর নির্বাণ পাওয়ার সফরে অনেক সাহায্য করেছিল বৈকি!
এরপর গৌতম উদ্রক রামপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই গুরু তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুর উপলব্ধির শিক্ষা দেন। কীভাবে নানা জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে দেখে-শুনে-চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে আসা লাগে - এই শিক্ষা পান তিনি উদ্রক থেকে। এটিও তিনি খুব দ্রুত আয়ত্তে নিয়ে আসেন। এই গুরুও একই প্রস্তাব দিলে গৌতম সেটিও ছেড়ে দেন। যোগ দেন আরো পাঁচজনকে নিয়ে কিঞ্চিৎ চরমরূপে সন্ন্যাসব্রতে।
একটি চালের দানায় এক দিন। এই ছিল এই সময়টায় তাঁর আহারমন্ত্র। শরীরের উপর অত্যাচার করেও তিনি খুব একটা লাভবান হচ্ছিলেন না। সত্যের জ্ঞানলাভ দূরেই থেকে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হতে লাগলো। ফলে তিনি এই সঙ্গ ত্যাগ করে আহারের এই চরম নিয়ম ত্যাগ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন। এবং বর্তমানে গয়াতে (তৎকালীন উরুবিল্ব) বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের (অশ্বত্থ বট) নিচে তপস্যায় বসে যান।
এখানেই গৃহত্যাগের ৬ বছরের মাথায় তিনি লাভ করেন নির্বাণ*। মহাজ্ঞান। গৌতম হয়ে উঠেন বুদ্ধ। সংসারে জীবনচক্রের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন। মোক্ষ লাভের দ্বার তাঁর কাছে খোলা। এই জ্ঞান বৃহত্তর মানব কল্যাণে ছড়িয়ে দিতে হবে - এই ধারণাটা আসে ব্রহ্মা থেকে। প্রথমে বুদ্ধ সন্দেহ পোষণ করছিলেন যে, এই জ্ঞান কি জগতের মানুষ নিতে পারবে কিনা। বৈদিক ধর্মের সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে বুদ্ধকে এই বিদ্যার প্রচারে ব্রতী হতে অনুরোধ করেন।
এরপর তিনি দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তাঁর লব্ধ জ্ঞান বিতরণ করে গেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বোধিসত্ত্ব এমন একটি সত্তা যিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তাঁরা সেটি সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ না করে পরিনির্বাণ গ্রহণ করেন না। মানুষের জন্য মমত্ববোধ থেকে তিনি নির্বাণ লাভের শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল দুনিয়াতে থেকে যান। তাঁর এই ত্যাগস্বীকারের জন্য তিনি মহৎ রূপে সকলের নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আর গৌতম হলো বোধিসত্ত্বের ধারার এক বুদ্ধ। শাক্যমুনি বুদ্ধ।
কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে অবশ্য পালনীয় নিয়ম-নীতি, আচার-বিধি থাকে, তেমন কিছুই তিনি বলেন নি। কেবল সকলকে দিতে চেয়েছেন দুঃখ হতে মুক্তি। নির্বাণের পথ। একটি সত্য, সহজ দর্শন।
তাঁর দেখানো পথের এই এক অদ্ভুত সুন্দর এক দিক। কোন সঠিক-বেঠিকের বিচার তিনি করতে যাননি। তিনি বাস্তবিক ও লাভজনক পথের দিশা দেখিয়েছেন। ঠিক-ভুলের হিসাব করতে গেলে তো তাঁর কথা ধর্মই হয়ে যেত। যেখানে একেকটি বানী একেকটি আপ্তবাক্য হয়ে উঠে। বুঝার আগে মেনে চলা চলে আসে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দর্শন ধর্ম না হলেও শীঘ্রই তা নিয়ম রীতির জালে পড়ে ধর্ম হয়ে উঠে। অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকার ফলে কেবল মুখে মুখে মনে রাখা তত্ত্বকথায় সবার কাছে বুদ্ধের কথা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। তৈরি হয় লিখিত গ্রন্থ। শুরু হয় বিভাজন*।
ধর্মবিভাজনঃ
তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকশ বছর পরে তাঁর দর্শন পরিপূর্ণ একটি ধর্ম হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ত্রিপিটকের তিনটি পিটকের [সূত্র (এখানে বুদ্ধের বক্তৃতা সন্নিবেশিত হয়েছে), বিনয় (এখানে সংঘের মেনে চলা উচিত এমন নীতির উল্লেখ আছে যা তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল), অভিধর্ম (তাঁর বানীর তর্জমা)] মাঝে একটিতে (বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট!) গণ্ডগোল লেগে যায়। সংস্কৃতজাত পালি ভাষার ত্রিপিটককে প্রাচীন ধরা হয়। আর দেড়শ-দুশো বছর নিরুদ্দেশ থাকার পর তিব্বতি ও চৈনিক ভাষাসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে আধুনিকতম কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ধারার উন্মেষ ঘটে। এছাড়া জাতক আরেকটি খুবই জনপ্রিয় গ্রন্থমালা। এখানে বুদ্ধের আগের অনেকগুলো জন্মের বৃহৎ ও সু-উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বানরদলের নদী পার হওয়া, বনে ক্রুদ্ধ রাজার সামনে ধ্যানমগ্ন সাধকের ধৈর্যের পরীক্ষা - এগুলো বিখ্যাত।
প্রথম দিকে ১৮/২০ টি বৌদ্ধমতধারার প্রচলন ছিল*। তবে মূল বিভাজন দুই শাখায়। তবে এদেরও বহু শাখায় বিভাজন ছিল এবং আছে।
১। মহাসাংঘিক। এর থেকে মূলত মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধমতবাদের সৃষ্টি। তাঁদের মূল মত হল গৌতম একজন অতিমানব যিনি স্বর্গ থেকে জগতের কল্যাণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাছাড়া মহাযান ও বজ্রযান মতধারা অনুযায়ী, যে কেউই বোধিসত্ত্ব অর্জন করতে পারে। আর এই অর্জনের পর মানবজাতির উপর দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উচিৎ যতদিন সম্ভব পরিনির্বাণের জন্য বিলম্ব করা। যাতে সাধারণের কাছে এই প্রজ্ঞাপারমিতা (অভিজ্ঞান) পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতে পারে।
চীন-জাপান-মঙ্গোলিয়াতে এর প্রচার মূলত বেশি। পশ্চিমা বিশ্বে এই মতবাদের জনপ্রিয়তা বেশি।
২। স্থবিরবাদ। এর থেকে মূলত থেরোবাদ বৌদ্ধমতবাদের সৃষ্টি। তাঁদের মতে, গৌতম সাধারণ মানুষ। কিন্তু কঠোর তপস্যা, গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিলেন। এই মতানুসারে, বোধিসত্ত্ব পেতে হলে সন্ন্যাসব্রত নেয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আর এর অর্জনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত কঠোর সন্ন্যাস উদ্যোগ। অরহৎ হয়ে গেলে কাউকে বলাটাও উচিৎ না বলে এই মতবাদমতে মেনে নেয়া হয়।
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এ মতের অনুসারী বেশি।
এছাড়া আরো কিছু মৌলিক বিষয়ে এই দুই মতবাদের বিরোধ আছে। যেমনঃ
- অরহৎ (নির্বাণ প্রাপ্ত তপস্বী) হবার পর কারো পক্ষে নৈতিক স্খলন সম্ভব কিনা, [স্থবিরবাদঃ সম্ভব]
- অভিধর্ম অংশের নানা আলোচনা, [সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিস্তৃত অভিধর্ম পিটকের অধিকারী স্থবিরবাদ]
- পুদ্গাল বা ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্কন্ধ বা ব্যক্তির ধ্যানধারণার মধ্যে কোনটি এক সত্তা হতে আরেক সত্তায় স্থানান্তরিত হয়, [স্থবিরবাদঃ ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই নেই]
- নৈতিকভাবে ভালো-মন্দ ছাড়া কাজের আর কোন ধরনের ফলাফল হতে পারে কিনা, [স্থবিরবাদঃ হয়, নির্লিপ্ত বা উদাসীন]
- সত্যের প্রাপ্তি কি তাৎক্ষণিক নাকি ধীরে ধীরে তা অর্জিত হয়, [স্থবিরবাদঃ তাৎক্ষণিক]
- সৎকর্ম কি অজান্তেই তৈরি হয় নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে জোর চেষ্টার দরকার হয় [স্থবিরবাদঃ ইচ্ছা করে, জোর করে তৈরি করতে হয়] ইত্যাদি।
- মহাযান
- থেরোবাদ
- বজ্রযান
 |
| Timeline of the Spread of Buddism [Source: Pinterest] |
 |
| Comprehensive Divisions of Three Major Sects of Buddhism [Source: Pinterest] |
বর্তমানে সাধারণের মাঝে বৌদ্ধ ধর্ম বলতেই যে চেহারাটা ভেসে উঠে তিনি হলেন দালাই লামা। মজার ব্যাপার হলো, ইনি কিন্তু বজ্রযানী বৌদ্ধের তিব্বত শাখার গেলুগ উপশাখার ধর্মীয় প্রধান। এবং বজ্রযান বিভাগ পুরো বৌদ্ধ জনসংখ্যার মাত্র ৬%*।
গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাঃ
ये धर्मा हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण
"ইয়ে ধারমা হেতু প্রাভাবা হেতুম তেষাম তাথাগাতো হ্যা ভাদাৎ,
তেষাম চা ইয়ো নিরোধা য়েভাম বাদি মাহাশ্রামাণাহ্"
"Of those phenomena which arise from causes:Those causes have been taught by the Tathagata (Buddha),And their cessation too - thus proclaims the Great Ascetic."
 |
| Source: International Buddhist Society |
নির্বাণ কী? বুদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য
"এক রাজা একবার বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিল, 'এক সাধকের সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায় কী?' বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, 'মনের সেই অবস্থা যখন সে পুকুরের টলটলে স্বচ্ছ পানি দেখতে পারে। পাহাড়ের উপর চড়ে গিয়ে পুকুরের তলার নুড়িপাথর, গাছপালা সে স্পষ্ট দেখতে পারে। পুকুরটা হলো বাস্তবতা।'"
শূন্যতা কী? বুদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি
शुन्पता करुणा गर्भम्
শূন্যতা কারুণা গার্ভাম
Emptiness is the Womb of Compassion
অর্থাৎ সহমর্মিতার দ্বারা বোধিসত্তা অর্জন করতে হলে আগে শূন্যতা অর্জন করতে হবে। এই শূন্যতার কথা গৌতম বলে গেছেন। কোন আলাদা অস্তিত্ব কারো নেই। সবাই একটি আদি ও অন্তহীন একটা অস্তিত্বের, একটি চক্রের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কোন বিগ ব্যাং বা ক্রাঞ্চের অস্তিত্ব নেই। এটাকেই বৌদ্ধ দর্শনে বলা হচ্ছে, সংসার বা সামসারা। এই চক্র বা সংসারে আবদ্ধ হয়ে যায় মানুষ যখন এর প্রতি যুক্ত হতে চায়। পার্থিব বস্তুর সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে দুঃখ পোহাতে হয়। যা তাঁকে আরো দুর্দশায় ফেলে দেয়। তাই এ থেকে মুক্ত হওয়া উচিৎ। মোক্ষ বা নির্বাণ পেলে এর থেকে মুক্তি। আর এর প্রথম ধাপ হলো এই শূন্যতার উপলব্ধি। একেকজন মানুষ বা যেকোনো অস্তিত্ব আলাদা কিছু না। সবকিছুকে ভাগ করলে যেমন একই প্রোটন- ইলেকট্রন পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু আদতে তাঁর ক্ষুদ্রতম বিভাজনে গেলে একই জিনিস। এই কথাটা দিয়ে বুদ্ধ চেয়েছেন, সবাই যাতে বুঝতে পারে প্রতিটি জীব এক অপরের সাথে যুক্ত। কেউ আলাদা কোন মানে রাখে না। ফলে একেকটি মানুষ একটি শূন্য খোলস মাত্র।
প্রফেসর থারম্যান এটাকে ব্যাখ্যা করেন কার্তেসীয় ব্যবস্থা দিয়ে। একটা বিন্দু আসলে x-y অক্ষে বিন্দু নয়, বৃত্ত। তাই সেই বৃত্তের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে বের করতে গেলে একদম সঠিক ভুজ ও কোটির মান বের করা সম্ভব না। সেটা করতে গেলে সেই বিন্দুর অস্তিত্ব আর থাকবে না। এই যে আসল জায়গাটা খুঁজে বের করতে গিয়ে সমস্ত অস্তিত্বটাই নাই হয়ে যাওয়া, এটাই বুদ্ধের শূন্যতা।
কেউ যদি ধ্যান শুরু করে এই চিন্তা করে যে সে এই শূন্যতাকে খুঁজে বের করবে, তাহলে সে আসলে তাঁর অস্তিত্বকেই বের করবে। কিন্তু সে এতে সক্ষম হবে না। কেননা, বুদ্ধের মতে অস্তিত্বটাই নেই। মানুষের খোল বদলায়, বড় হয়, বয়স হয়। মনের গভীরে যে পরিচয়টা সে ধারণ করে, যে বিষয়টা আমাকে 'আমি' করে তুলে সেটা আসলে কিছু না। কিছু না থাকা থেকে এই শূন্যতা।
এই যে না থাকার অনুভূতি ও নিরাসক্তি এই ধারণা কিন্তু বাউলধারাতেও মেলে। সত্যিকারের মৃত্যুর আগেই কেউ যদি সেই শূন্যতা অনুভন করে ফেলতে পারে, তবেই জন্ম সার্থক। যেমনটা বলে গেছেন, কবির তাঁর দোঁহাতেঃ
ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা -- অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো
সত্গুরু সঙ্গত তরতা হৈ -- সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হিংসা -- কবীর বলেন, কোথায় সেই বিরল হংসসাধক
জীবতাহী জো মরতা হৈ। -- জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছে যে
আবার বাংলার লালন ফকির গানে গানে বলেনঃ
মরার আগে মরে
শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন,
মুরশীদ ধরে জানতে হয়।
আবার পারস্যের লোকপ্রিয় সূফী কবি জালালউদ্দিন রুমী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মসনবী' তে তোতা কাহিনীতে বলেন,
"মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। তাই মরার আগে মরবার চেষ্টা করো"
এরকম সব সাধকদের মাঝে একই কথা উচ্চারিত হলেই যে তা সত্য হয়ে যায় তা কিন্তু না, বরং বিষয়টা এই জিনিসটাই প্রমাণ করে যে, আলাদা আলাদাভাবে ভাবের সাধনা করে একটি সুন্দর মতবাদে অনেক পথ ধরে এসেই মিলিত হওয়া যায়। এখানেই এই দার্শনিক কথার সার্থকতা ও সৌন্দর্য।
কার্মা (কর্ম) ও ধার্মা (ধর্ম) কী?
অষ্টমার্গ
প্রজ্ঞাঃ
নৈতিকতাঃ
|
মাধ্যম |
অকুশলী
উপায় |
কুশলী
উপায় |
|
দেহ |
জীবন
নেয়া |
জীবন বাঁচানো |
|
চুরি
করা |
উপহার দেয়া |
|
|
কামের
অমার্জিত ব্যবহার |
কামের সুব্যবহার |
|
|
বাক্য |
মিথ্যা
বলা |
সত্য বলা |
|
বিভেদের
কথা বলা |
সম্মিলনের কথা বলা |
|
|
কঠোর
কথা বলা |
নরম সুরে কথা বলা |
|
|
অর্থহীন
কথা বলা |
প্রকৃত অর্থপূর্ণ কথা বলা |
|
|
মন |
লোভ
করা |
উদার হওয়া |
|
হিংসা
করা |
কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা |
|
|
অন্যের
সম্পদের লালসা |
সন্তুষ্টি |
|
|
ঘৃণা
বা ক্ষতি করার মনোভাব |
প্রশংসা করা |
|
|
অবাস্তব
দৃষ্টিভঙ্গি |
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও খোলা মন |
সমাধি বা ধ্যানঃ
ENLIGHTENED = REALISTIC + DECENT + IN CONTROL OF YOURSELF
সহমর্মিতাঃ বুদ্ধত্ব অর্জনের পূর্বশর্ত
"যদি যার যার দুঃখ তার তারই সামলাতে হতোতবে পায়ে ব্যথা পেলে হাত এগিয়ে যায় কেনো?"
দালাই লামা (১৪তম) বলেন,
"যদি সুখী হতে চাও, অন্যের দুঃখে সহমর্মী হও"
"স্বার্থপর যদি হতেই চাও, তবে জ্ঞানীর মতো হও। সমবেদনা তৈরি করো। কারণ সমব্যথী হওয়ার জন্য যে শান্তির অনুভূতি আসে সেটা নিজেরই হয়। অন্যের না।"
মজার ব্যাপার হলো, মহাযানী রীতিমতে এই শান্তিদেবকে নালন্দাতে ভুসুকু বলা হত। ভুক্তি, সুপ্তি, কুটির। অর্থাৎ কুটিরে থেকে থেকে কেবল খাওয়া আর ঘুম ছাড়া সে কিছু করতো না। কিন্তু তিনি আদতে এ বিশাল বইখানা এই সময়ে লিখেন। আবার, বাংলার আদিতম নিদর্শন চর্যাপদে এক বাঙালি কবির সন্ধান পাওয়া যায়। যার নাম ভুসুকুপা। পদ রচনা করত দেখে নামের শেষে পা। দুইজন একই কিনা এ নিয়ে ভালো মতবিরোধ আছে।
"আপনা মাংসে হরিণা বৈরি" নামে যে প্রবাদ আছে বাংলায় যে হরিণের মাংসই হরিণের শত্রু - এটি তাঁরই লিখা। আবার তাঁর বাঙ্গালিয়ানার পরিচয় যেই পদ থেকে মেলে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এবং সন্দেহ যুক্তিযুক্ত। মল্লরী রাগে গেয় ৪৯ নং চর্যায় বলে,
ণাব পাড়ী পউআঁ খালে বাহিউ।।
অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চন্ডালে লেলী
আধুনিক বাংলাঃ
বজ্রনৌকা বেয়ে পাড়ি দেই পদ্মা খাল,দেশ লুট ক’রে নিল অদয় বঙ্গাল।ভুসুকু, বাঙালি হলি আজ থেকে ওরে,নিজের ঘরনি গেল চাঁড়ালের ঘরে।
বাঙালি তো নয়ই বরং বাঙ্গালিয়ানাকে যেন খানিকটা বিদ্রূপই করছেন পদকার। সে যুগে সারকাজমের চর্চা বা নিজের বেহাল দশা নিয়ে চুটকি করার অভ্যাস থেকে থাকলে - সেই অর্থ বিবেচনায় ভুসুকুপা বাঙালি বটে।
বৌদ্ধ মতবাদের রাজনীতিঃ
অশোকের বৌদ্ধ মতবাদ গ্রহণ ও ধর্ম প্রচারঃ
 |
| সাঁচির বিখ্যাত স্তূপ [Source: Maps of India] |
 |
| সারনাথের অশোক স্তম্ভের মাথার সিংহ চতুর্মুখ যা বর্তমানে ভারতের জাতীয় প্রতীক, সিংহের পায়ের নিচে ২৪ স্পোকওয়ালা অশোক চক্র যা ভারতের পতাকার মধ্যে দেখা যায়। চক্রের দুই পাশে চারটি প্রাণীও আছেঃ গরু, ঘোড়া, হাতি ও সিংহ। [Source: Pinterest] |
"আমার প্রজারা যতক্ষন না ধর্মের পথে থেকে সঠিকভাবে এর চর্চা করবে ততক্ষণ আমার কোন যশ বা খ্যাতিকে আমি বড় করে দেখবো না। সেটা বর্তমান বা ভবিষ্যতে যখনই হোক। আমি কেবল এই এক জিনিসের জন্যই পরিচিতির আশা করি। আর আমি যতকিছু করে যাচ্ছি তার সবই আমার জনগণের কল্যাণের জন্য, তারা যাতে পরের জন্মে আরো কম পাপ করে........." মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ১০
|
১-অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) |
২-সংস্কার (অবচেতন) |
৩-বিজ্ঞান (মনন) |
|
৪-নাম ও রূপ (উপলব্ধির স্বরূপ) |
৫-ষটেন্দ্রিয় (৬ ইন্দ্রিয়) |
৬-স্পর্শ |
|
৭-বেদনা (অনুভূতি) |
৮-তৃষ্ণা (আকংখা) |
৯-উপাদান (ধরে রাখা) |
|
১০-ভব (অস্তিত্ব) |
১১-জাত (জন্ম) |
১২-জরমরণ (ব্যাধি ও মৃত্যু) |
অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যঃ
অহিংসাঃ
কোনভাবেই হিংস্রতা বা অত্যাচারের বশবর্তী না হওয়া বুদ্ধের প্রচারিত শিক্ষার অন্যতম অংশ। জীবহত্যাকে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে প্রকৃতির কোন জীবন মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শিকারকে অপ্রয়োজনীয় বলা হয়েছে। কারণ এটা অহেতুক হত্যা এবং সেই সময়ে অভিজাতরা শিকারকে অবসর বিনোদন হিসেবে নিতো। শাকাহারী হওয়াকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সম্রাট অশোক চেয়েছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যে প্রাণীহত্যা যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হোক। তিনি খোদাই করে দিয়েছেন,"আমার রসুইয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার প্রাণী হত্যা করা হত কেবল তরকারি রাঁধার জন্য। কিন্তু এখন এই আদেশনামা লেখার সময়ে কেবল তিনটি প্রাণীর জীবন নেয়া হয়েছে। দুইটি ময়ূর ও একটি হরিণ। হরিণটা তাও মাঝে মাঝে। এবং খুব শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন এই তিন প্রাণীও আর মারা হবে না" -মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ১
"...আগে আমি যখন হিংসার আশ্রয় নিয়ে আমার কাজ সারিয়ে নিতাম তখন কোন স্বর্গীয় বা শান্তির চিহ্ন আমি দেখতাম না। কিন্তু এখন অহিংসার পথ ধরার পর থেকে চারপাশে কেবল স্বর্গরথ, ঐরাবতের মতো ঐশ্বরিক প্রতীক দেখতে পাচ্ছি..." - মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ৪
"...এই কাজগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা যায়ঃ হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার - এগুলো দিয়ে আমার ধ্বংস যাতে না হয়..." - মুখ্য স্তম্ভাদেশ নং ৩
শিক্ষাতত্ত্বঃ
"আমার রাজত্বের প্রতিটি অংশের শাসকদের পাঁচ বছর পর পর ধর্ম প্রচারের (ও অন্যান্য সকল কাজের) জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সফর করতে হবে। তাঁদের যে শিক্ষাগুলো প্রচার করতে হবে তা হলঃপিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রশংসনীয়,বন্ধু, স্বজন, পরিচিত, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের প্রতি উদারতা প্রশংসনীয়,জীবহত্যা থেকে বিরত থাকা প্রশংসনীয়,ব্যয় ও সম্পত্তি অর্জনে পরিমিত হওয়া প্রশংসনীয়......" - মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ৩
"ধর্মের পথ সবচেয়ে বাহবা পাওয়ার যোগ্য। এখন ধর্মের কাজ কী কী? এগুলো হলঃ পাপের কাজ কম করা, অনেক নৈতিক ভালো কর্ম, সমবেদনা, উদারতা, সত্যবাদিতা ও মনের শুদ্ধতা..." - মুখ্য স্তম্ভাদেশ নং ২
উল্লেখ্য, তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি মহামাত্র বা মন্ত্রীও নিয়োগ দিয়েছিলেন, যাদের কাজ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বা দর্শনের ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি জৈন, ব্রাহ্মণ ও অজীবক সন্ন্যাসীদের সরাসরি দেখভাল করা।
নিঃস্বার্থ পরোপকারিতাঃ
"আগে রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন সংবাদ বা দরকারি খবর সম্রাটকে সবসময় দেয়া হতো না। কিন্তু এখন আমি আদেশ দিচ্ছি, যদি আমি খাওয়ার মাঝে থাকি, বা নারীদের মহলে থাকি, অথবা শোয়ার ঘরে থাকি, কিংবা রথে/পালঙ্কে/বাগানে - যেখানেই থাকি না কেন কর্মচারীরা প্রজাদের কোন সংবাদ বা রাজ্যের কোন প্রতিবেদন নিয়ে যে কোন সময়ে, যে কোন জায়গায় আমার কাছে আসবে। যাতে আমি সবসময় সেদিকে নজর রাখতে পারি। আর যদি মহামাত্রদের (ধর্ম প্রচার, নীতি নির্ধারণের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) মাঝে আমার দেয়া কোন নির্দেশ, কাজ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সেটা যেন আমাকে অবিলম্বে জানানো হয়..." - মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ৬
সাম্যবাদঃ
"সকল গোষ্ঠীর উন্নতি হওয়া জরুরি। এবং তা অনেক উপায়েই করা যায়। কিন্তু এর মূলটি রয়ে গেছে কথার লাগামে। মানে, কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া নিজের ধর্মকে বড় করে দেখানো এবং অন্যের ধর্মকে ছোট করা। যদি সমালোচনার কিছু থেকেও থাকে সেটা নরমভাবে করা। কিন্তু এজন্য অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করাটাই ভাল। এর মাধ্যমে নিজের ও অন্যের ধর্মেরই ভাল হয়। আর এক অপরের ধর্মকে সম্মান না করলে দু ধর্মেরই ক্ষতি হয়। কেউ যদি অন্ধভক্তির কারণে নিজের ধর্মের সম্পর্কে অতি উৎসাহী হয়ে অন্য ধর্মের লোককে নিন্দা করে আর বলে 'আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ' তবে সে নিজের ধর্মেরই ক্ষতি করে... সকলের উচিৎ অন্যদের মতামত ও চিন্তাধারা মনোযোগ দিয়ে শোনা......" - মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ১২
"সম্রাট চান, যেন সব ধর্ম সব জায়গায় থাকে। কেননা প্রতিটি ধর্মই চায় আত্মসংযম ও হৃদয়ের শুদ্ধতা। কিন্তু অনেক চিন্তাধারার ও মন-মানসিকতার মানুষ আছে যারা হয় তাঁর ধর্মের পুরোটা গ্রহণ করে বা কিছু অংশ নেয়। তাই যারা এমন মহান শিক্ষা পেয়েও কৃতজ্ঞতা, সংযম, শুদ্ধাচারের চর্চা করতে পারে না, তারা অধম।" - মুখ্য প্রস্তরাদেশ নং ৭
"আমি, সম্রাট অশোক, সুস্থ চিত্তে আমার সাম্রাজ্যের সকল সম্পত্তি সংঘগুরু উপগুপ্তকে দিয়ে যাচ্ছি।"
বলা হয়, এই আমের খোসার উইলে অশোক তাঁর সিংহ সিলও লাগিয়ে ছিলেন। তাঁর দাঁতের সাথে ছোট একটা সিংহের মাথার নকশার টুপি লাগানো থাকতো। এটাই তাঁর দপ্তরের সিলমোহর ছিল। তিনি আমের খোসার উপর কামড় দিয়ে সেই সিল দিয়ে দেন এবং সংঘের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। একদিন তাঁর জানালার কাছ দিয়ে সংঘের এক দল মুষ্টিভিক্ষার কাজে বের হয়েছে। তিনি জানালা দিয়ে তাঁর আমের খোসার উইল ছুঁড়ে মারেন। সন্ন্যাসী সেটি উপগুপ্তের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু উপগুপ্ত বুঝতে পারে এই নির্দেশ মেনে নিলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাছাড়া এতো অর্থ-সম্পদ ব্যবস্থাপনা করার জন্য ইচ্ছা, ধর্মীয় অনুশাসন, জ্ঞান কোনটাই তিনি বাস্তবিক বলে মানতে পারলেন না। ফলে তিনি সেই উইল নিয়ে মন্ত্রীদের কাছে এলেন ও এই উইল প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে অশোকের জাগতিক সম্পদ সংঘের উন্নয়ন কাজে ব্যয় হবার ইচ্ছা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।
এগুলো ছাড়াও অশোকের সময়ে সংঘগুলোতে সহজিয়া রীতির পদ বানিয়ে গান গেয়ে পরিবেশন করা হতো বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা দিয়ে থাকেন।
"পদ্মের পাতায় পানি যেমন, যেমন সুঁইয়ের ডগায় সরিষা,
ব্রাহ্মণ বলি তাঁরে - যেজন তেমনি ধরে রাখে সুখটারে।"
আবার-
"সর্বোচ্চ প্রাপ্তি স্বাস্থ্য, সন্তুষ্টি হলো শ্রেষ্ঠ ধন,
কাছের আত্মীয় বিশ্বাস আর সেরা সুখ নির্বাণ।"
তবে অশোকের এই বুদ্ধনীতি প্রচারের বড় একটা প্রভাব পড়ে সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ ব্যবস্থায়। সক্রিয় সেনার সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যুর ৪০-৫০ বছরের মাঝে মৌর্য সাম্রজ্যের পতন ঘটে বাইরের ও ভিতরের শত্রুদের আক্রমণে। তবে সংঘ সমাজ বেঁচে থাকে যুগের পর যুগ ধরে।
বুদ্ধ মতের যুগে যুগে বিবর্তন
জন্মভূমিতে বৌদ্ধ দর্শনের বিলোপঃ
তিব্বতে বৌদ্ধবাদঃ
দর্শনটির জন্মস্থল একে ধরে না রাখতে পারলেও হিমালয় পাড়ি দিয়ে এটি প্রধান আকর্ষণ হিসেবে জায়গা করে নেয়। এর পেছনে অনেকগুলো ব্যাপার কাজ করেছে। কেন পূর্বে বা পশ্চিমে না ছড়িয়ে হিমালয় পাড়ি দিয়ে উত্তরে এতো উঁচুতে বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার লাভ করলো। এর জন্য দায়ী রাজা সোংসেন গামবো। তিনি ভারত থেকে বৌদ্ধবাদের বই নিয়ে আসতে থাকেন ও তিব্বতি ভাষায় শুরু হয় এর অনুবাদ। এর কাজ শুরু হওয়ার জন্যই পরে যখন অনেক বই হারিয়ে যায় ভারত থেকে, সেগুলোর অস্তিত্ব তিব্বতে বহাল তবিয়তে পাওয়া যায়। আর এই ভাষান্তর করার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশার সৃষ্টি হয়। লোৎসাওয়া। বা অনুবাদক। এর আক্ষরিক অর্থ বিশ্বের চোখ। মানে তাবৎ বিশ্ব থেকে আহরিত জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। আর এই লোৎসাওয়ারাই পরবর্তীতে বিভিন্ন মতধারার প্রচারক ও বাহক হিসেবে তিব্বতে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও আলোচিত পদ্মসম্ভব ও রিনচেন জাংবো। তিব্বতের প্রতিটি শাখাই কোন না কোন তন্ত্র সাধনা করে থাকে। বজ্রযান এসেছে এই তান্ত্রিক যোগসাধনা থেকেই। আর প্রতিটি শাখার পদ্ধতি নিয়ে মূল খুঁজতে গেলে কোন না কোন মহাসিদ্ধ বা তন্ত্রসাধকের লেখার রেফারেন্স পাওয়া যায়।
পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে অন্য রকমের সম্মান দেয়া হয়। অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা ত্রিসোন ডেটসেনের আমন্ত্রনে তিব্বতে আসেন ও তাঁর সময়েই তিব্বত বর্ণমালা ও ব্যাকরণের কাজ করা হয় যাতে সংস্কৃত থেকে এ ভাষায় বৌদ্ধ মতবাদের কথাগুলো নিয়ে আসা সহজ হয়। এই পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে দ্বিতীয় বুদ্ধ বলা হয়। তাঁকে গুরু রিনপোচে নামে সম্মানিত করা হয়। তিব্বতে অনেক জন রিনপোচে (মানবরত্ন) আছেন। কিন্তু কেবল রিনপোচে সম্বোধনে তিনজন সাধককে একনামে সবাই চিনে। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলো এই পদ্মসম্ভব। গুরু রিনপোচে। আর বাকিরা হলেন, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর বা জো রিনপোচে এবং জে সংখাপা বা জে রিনপোচে - যিনি গেলুগ শাখার আদিপুরুষ।
 |
| তিনজন রিনপোচে [Source: Gar Drolma, Garywonghc, Universal Compassion Foundation] |
এই পদ্মসম্ভব উড়িষ্যার মানুষ ছিলেন*। এবং তাঁর করে যাওয়া কাজের উপর ভিত্তি করে ন্যিংমা মতবাদের শুরু হয়। ন্যিংমার আক্ষরিক অর্থ প্রাচীন। কারণ এটি তিব্বতি বজ্রযানী ধারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। এই ধারার মতে, যোগচেন বা অতিযোগের মাধ্যমে বুদ্ধচিত্ত অর্জন করা যায়। মোক্ষ লাভ করতে হলে, ন্যিংমা মতানুসারে, এই অতিযোগের মাধ্যমে অসামান্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে। আর তার জন্য দরকার অতি সূক্ষ্ম মনোযোগ সহকারে মনের মধ্যে ছবি জাগিয়ে তুলে যোগসাধনা করা। তন্ত্রের চর্চা করা। এই ন্যিংমা মতবাদের সকল ধারার আদিপুরুষ হিসেবে পদ্মসম্ভবকে মেনে নেয়া হয়।
সময়ের সাথে সাথে তৈরি হয় নানাবিধ বৌদ্ধ মতবাদ। কাগ্যু ধারা, যা চট্টগ্রামের স্থানীয় তিলোপার শিষ্য নারোপার থেকে তিব্বতে নিয়ে আসেন মারপা,আরেকজন লোৎসাওয়া। মহামুদ্রার এই শিক্ষাকে জনপ্রিয় করেন মিলারেপা যিনি তাঁর গুরু মারপাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে কাগ্যু ধারাকে তিব্বতের সবচেয়ে বড় শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য, এই মিলারেপা সিদ্ধ হবার আগের জীবনে অত্যন্ত রাগী ও রুক্ষমেজাজি ছিলেন। ৩৫ খুনের দাগ ছিল তাঁর নামে। কিন্তু তিনি এতোটাই বুঁদ হয়ে বুদ্ধ তপস্যায় লেগে যান যে, তিনি এক জীবনের সময়েই বোধিসত্ত্বা অর্জন করেন। এই অর্জন তান্ত্রিক ধারাকে আরো মজবুত করে এবং মিলারেপা হয়ে উঠেন কিংবদন্তী। মিলারেপা তাঁর শিক্ষাগুলোকে পদাকারে গাইতেন। অনেকটা চর্যাপদের সহজিয়া পদাবলীর মতো। একই ধারণা প্রসূত। কেননা বজ্রযানী ধারনাগুলোর বেশিরভাগ উৎস ছিল বাংলার সিদ্ধরা যারা বিহারগুলোতে শিক্ষাগুরুর কাজ করতেন। এই মিলারেপা নিয়ে অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি নাকি বাতাসের বেগে উড়ে বেড়াতে পারতেন। আবার তিনি নাকি হিমালয়ের মাথায় গিয়ে কেবল একটি সুতি কাপড় গায়ে জড়িয়ে তপস্যা করতেন। তাঁর ছিল ৫টি বিশেষ তান্ত্রিক যোগশিক্ষা।
1. Magic body 2. Inner fury fire 3. Lucid dream yoga 4. Death soul ejection 5. Clear light immersion
এই কাগ্যুধারার আবার কিছু শাখা আছে যার একটি হল কারমা। এই শাখার মাহাত্ম্য হলো, ত্রয়োদশ শতকে এই কারমা ধারাতেই বৌদ্ধ মতবাদে পুনর্জন্মের ঘটনা ঘটে প্রথমবারের মতো। কর্মপক্ষী, এক বিস্ময়বালকের জন্ম হয় যে আগের কারমাপার ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিখুঁতভাবে খুঁজে নেয় ও সংঘে যেয়ে তাঁর শিষ্যদের বৌদ্ধ মতবাদের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। এই অভূতপূর্ব ঘটনার জন্য তাঁকে দ্বিতীয় কারমাপা হিসেবে মেনে নেয়া হয় এবং পুনর্জন্মের এই ব্যাপারটা বজ্রযানে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই বারংবার পুনর্জন্ম নেয়ার ধারাটিকে তখন অবলোকিতেশ্বর বা চেনরেজিগের অবতার হিসেবে ধারণা করা হয়। এই অবলোকিতেশ্বর একজন প্রখ্যাত বোধিসত্ত ছিলেন। যুগে যুগে এই অবতারের আগমনের কারণে মানুষ দিকভ্রষ্ট হওয়া থেকে নিস্তার পায়। এবং একই সাথে একজন মূর্তমান বোধিসত্ত নিজেদের সমাজে, মানুষের মাঝেই বিরাজমান আছে - এই ধারণা মানুষের মনে সাহস যোগায় ও ভরসা দেয় যে, তারাও এক জীবনেই বোধিসত্ত অর্জনে সক্ষম হতে পারে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো শাক্যধারা। এই ধারার মাহাত্ম্য হলো এই শাখার মাধ্যমেই মঙ্গোলিয়ার সাথে তিব্বতের প্রগাঢ় সম্পর্ক শুরু হয়। এর প্রবর্তক হিসেবে ধরা হয় পাঁচজন মহামুনিকে। সাচেন কুঙ্গা, সোনাম সেমো, জেৎসুন দ্রাগপা, শাক্য পণ্ডিত, ফাগপা। এই ফাগপা কুবলাই খানের (চেঙ্গিস খানের নাতি যিনি চীনে ইউয়ান রাজবংশের শুরু করেন) ধর্মীয় গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। এই সময় থেকেই তিব্বতে ধর্মীয় গুরু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন কারণ কুবলাই খান তাঁকে এই সুযোগ করে দেন।
বিরূপা শাক্য ধারার মতবাদের একজন বিখ্যাত সাধক। তাঁর প্রচারিত শিক্ষা থেকেই শাক্য ধারার মতবাদগুলো এসেছে বলে ধারণা করা হয়। তিনিও বাঙালি ছিলেন। বলা হয়, তিনি এক শুঁড়িখানায় যেয়ে মদ খেতে চান এবং এর খরচ সূর্য ডুবার পর চুকিয়ে দেবেন এই শর্তে খাওয়া শুরু করেন। কিন্তু বিকেলের পর তিনি আঙ্গুলের ইশারায় সূর্যকে ডুবা থেকে আটকে রাখেন। ফলে রাজা এসে তাঁর মদের খরচ চুকিয়ে দিলে তিনি ঠাণ্ডা হন।
 |
| বিরূপার সূর্যাস্ত আটকে দেবার বিখ্যাত ঘটনা [Source: Pinterest] |
সবচেয়ে নতুন ধারার নাম গেলুগ। যা মূলত অতীশ দীপঙ্করের শিষ্য দ্রোমতনের প্রচারিত মতামত থেকে নেয়া। কদম ধারা খুব শীঘ্রই আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। কোনটা আদিগুরুর মুখের কথার সূত্র ধরে, কোনটা লিখে রাখা সূত্র ধরে। এগুলোকে একীভূত করে ও অন্যান্য ধারার উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা নিয়ে জে সংখাপা চালু করেন গেলুগ ধারা সেই চতুর্দশ শতাব্দীতে। তিনি এই মতধারার শিখাগুলো লিখে যান তাঁর লামরিম চেনমো নামের বইয়ে। এই বইটির মূলতত্ত্ব আছে অতীশ দীপঙ্করের বোধিপথপ্রদীপ নামের সংস্কৃত বইয়ে। জে রিনচেন বলেন, বোধিসত্ত অর্জনের জন্য মানুষের দরকার তিনটি পথ অবলম্বন করা - সংসার ত্যাগের ইচ্ছা, সকল জীবের জন্য বোধিচিত্ত অর্জন করা [মহাযান তত্ত্ব], শূন্যতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারা। এগুলোর সাথে বজ্রযান ধারার ধ্যানের অবলম্বন করার মাধ্যমে দ্রুত বোধিচিত্ত অর্জন করা সম্ভব বলে জে সংখাপা মত প্রকাশ করেন।
তিব্বতি বৌদ্ধ মতবাদ এতো বেশি পথ-মতবাদ-চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে বছরের পর বছর নানাভাবে রূপ নিয়েছে যে সবগুলোর সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা অর্জন করা ও এখানে আলোচনা করা অসম্ভব। তাছাড়া, বিভিন্ন বৈদিক ও তিব্বতের স্থানীয় দেবতাদের সংযোজনে এই ধারাটি হয়ে উঠে চরম বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে একটি কথা সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিব্বতের সকল বৌদ্ধ মতবাদের প্রধান লক্ষ্য হলোঃ প্রজ্ঞাপারমিতা বা চরম জ্ঞান লাভ করে, তন্ত্রে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে সংসারের চক্র থেকে মুক্তি লাভ করা। বোধিচিত্ত অর্জন করা।
আর একই সাথে তিব্বতের বৌদ্ধ মতবাদ বাকি অন্য যেকোন জায়গা থেকে ভিন্ন কারণ এটিই একমাত্র জায়গা যেখানে শত শত বছর ধরে সকল জনগণ একসাথে একই রকম আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে বৌদ্ধ দর্শনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার থেরোবাদ ও পূর্ব এশিয়ার মহাযান - এসব জায়গায় সামাজিক ও আত্মিক ধারণায় বুদ্ধ যেভাবে ঢুকে আছে তার চেয়ে বহুগুণে প্রভাবান্বিত তিব্বতিরা। দলে দলে নিজের ইচ্ছায় সামরিক আগ্রাসনের থেকে সরে এসে শান্তিপূর্ণ ভাবে কৃষিকাজ ও পশুচারনার মাধ্যমে জীবিকা ও জীবন নির্বাহ করে যাওয়া এই তিব্বতিরা প্রকৃতার্থে উচ্চতর মানসিকতা ও সভ্যতার জানান দেয়। নারীর সমতা, সম্পদের বণ্টন ও বস্তুবাদে আসক্ত না হয়ে ভাববাদ-বৌদ্ধবাদে বুঁদ হয়ে থেকে সংসার থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এর মাধ্যমে নির্ঝঞ্ঝাট একটি উন্নত জীবন ধারণ করা সম্ভব। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিব্বতিদের সংগ্রাম। এটা সত্যি যে গণহারে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করার মাধ্যমে যেকোন দেশ বহিরাগত সেনা হামলার বিপক্ষে একদম দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাই তিব্বতি বৌদ্ধদের ইচ্ছা। এতেই ওদের আত্মিক উদ্বোধন। তাদের এই ভাববাদের স্তর এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, "কেমন আছেন?" এই সরল প্রশ্নের উত্তরে তারা বলতোঃ
MA SHI TSAM LAH >> JUST BARELY NOT DEAD
তিব্বতে বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার হয়েছে দুই ধাপে। প্রথম ধাপে কিছু মঠ স্থাপিত হলেও দুশো বছর পড়ে আবার অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনা যেতে থাকে। এই ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ সজ্জা ছিল দেড়শ বছরের মতো। সোংসেন গামবো সপ্তম শতাব্দীতে প্রথম ধাপে কিছুটা সফল হলেও দ্বিতীয় ধারার স্ফুরণের পর আর কোন কারণে আটকায় নি। সেই ১০ম শতাব্দীর শেষ দিকে। তিব্বতের মানুষই যুদ্ধ-বিগ্রহ, ক্ষমতার টানাটানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে ও ধীরে ধীরে শুরু হয় বজ্রযানের ব্যাপক উত্থান। সেই ন্যিংমা থেকে শুরু করে একে একে গেলুগ পর্যন্ত। যা এখনো চলছে। এমনকি এখনো নিত্য নতুন শাখার তৈরি হচ্ছে। বিনয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকার ফলে বৌদ্ধ মতবাদে অনেকগুলো শাখা দেখতে পাওয়া যায়।
দালাই লামাঃ
জে সংখাপা পুনর্জন্মের পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই জানা যায়। তাঁর প্রধান শিষ্যরা দিকে দিকে গেলুগ মতবাদের শিক্ষা প্রচার করতে থাকে। গেদুন দ্রোপা ও খেদ্রুপ জে এই সময়ে প্রধান ছিলেন। দ্রোপার মৃত্যুর পর কারমাপার মতো এক বিস্ময়বালকের জন্ম হয়। গেন্দুন গ্যিয়াৎসু। তিনি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে সবার মধ্যে সাড়া ফেলে দেন। তাঁকে দ্বিতীয় দালাই লামা ধরা হয়। কিন্তু সেই সময়ে দালাই লামা বলা হতো না গেলুগ ধারার প্রধানকে। তৃতীয় হিসেবে যাকে ধরা হয়, সেই সোনাম গ্যিয়াৎসুকে এই উপাধি দেয়া হয়। আর সেটি করেন মোঙ্গোলদের একটি অংশের খান,আলতান খান। ষোড়শ শতকে তিনি তিব্বতি গেলুগ শাখার প্রতির আকৃষ্ট হয়ে সোনাম গ্যিয়াৎসুকে মঙ্গোলিয়ায় আমন্ত্রন জানান। সেখানে তিনি নিজেকে শাক্য পণ্ডিত ফাগপার পুনর্জন্ম হিসেবে দাবি করেন। আগেও বলা হয়েছে, এই ফাগপাই কুবলাই খানকে বজ্রযান বৌদ্ধ মতবাদে দীক্ষা দেন। ফলে, কুবলাই খানের বংশধর হিসেবে আলতান এতে প্রভাবিত হোন এবং গেলুগ মতবাদ গ্রহন করে নেন। যার ফল হিসেবে এখনো মঙ্গোলিয়ায় এই ধারার প্রভাব বেশি দেখা যায়। সোনাম গ্যিয়াৎসুকে তিনি উপাধি দেন দালাই লামা। দালাই হলো মঙ্গোলীয় ভাষায় সমুদ্র। দালাই শব্দটা আসলে তিব্বতের গ্যিয়াৎসু শব্দের মঙ্গোলীয় সংস্করণ। সেই থেকে দালাই লামা নামটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, তৃতীয় দালাই লামা আর তিব্বতে ফেরেননি এবং চতুর্থ দালাই লাম হিসেবে নির্বাচিত হন আলতান খানের নাতি।
এই জন্মান্তরের ধারায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হলো পাঞ্চেন লামা। ইনি গেলুগ ধারার এক অন্যতম ধর্ম গুরু। এবং তাঁর প্রধান একটি কাজ হলো, পরবর্তী দালাই লামাকে খুঁজে বের করা। এবং দালাই লামাই পরবর্তী পাঞ্চেন লামাকে খুঁজে বের করেন। ৫ম দালাই লামা এই গেলুগ ধারার অভূতপূর্ব সংস্কার করেন এবং এই পরস্পর নির্ভরশীল দায়িত্বের শুরু করেন। তিনি ১ম পাঞ্চেন লামা হিসেবে খেদ্রুপ জেকে স্বীকার করে নেন। আবার তিনিই প্রথম দালাই লামা যিনি সমগ্র তিব্বতের উপর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক - উভয় ক্ষমতার অধিকারী হন। এখানে একটি ছোট সংঘাতের কাহিনী আছে। ষোড়শ শতকে তিব্বতে গৃহযুদ্ধ লেগে যায়। কাগ্যু ও গেলুগ ধারার লামাদের সাথে জড়িত হয়েই বিভিন্ন অভিজাত পরিবার তিব্বতের শাসনকাজ চালাতো। তো এই গৃহযুদ্ধে গেলুগদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মঙ্গোল খান, গুশি খান। তিনি কাগ্যু ধারার শাসককে পরাজিত করেন ও ৫ম দালাই লামাকে পুরো তিব্বতের দায়িত্ব দেন। সালটা ১৬৩৭। এজন্য লোবসাং গ্যিয়াৎসুকে শুধু 'মহান পঞ্চম' বলেও ডাকা হয়। এরপর থেকে মোটামুটি দালাই লামাদের নির্বিঘ্ন সময় কাটতে থাকে। যদিও মাঝে তিব্বতের ক্ষমতা পুরোপুরি লামাদের হাতে ছিল। কিন্তু বড়সড় ঝামেলা বাঁধে কমিউনিস্ট চীনে এসে।
মিং ও কিং সাম্রাজ্যের সময়ে মোটামুটি শান্তি ছিল। যদিও ব্রিটিশ আক্রমণের জন্য ও চীনের কিং সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী সুশির (Cixi) সময়ে ত্রয়োদশ দালাই লামাকে বেশ কিছু বছর ছন্নছাড়া থাকা লাগে। কিন্তু সুশি মারা যাবার পর সান ইয়াৎ সেনের সময়ে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। এবং ত্রয়োদশই তিব্বতের জাতীয় পতাকার নকশা করেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু লিন সেনের (কুয়োমিন্তাং চীনের চেয়ারম্যান) সময়ে এই ত্রয়োদশ দালাই লামা একটি অদ্ভুৎ কাজ করেন এই সময়ে। তিনি বলেন, সামনে তিব্বতের গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। তা মোকাবেলা করতে তাঁর দেহত্যাগ করে নতুন দেহে, যুবক শরীরে ফিরে আসতে হবে। তাই তিনি স্বেচ্ছায় যোগবলে মৃত্যুবরণ করেন এবং এর দু বছর পরেই উত্তর পূর্ব তিব্বতে জন্ম হয় তেনজিন গ্যিয়াৎসুর। চতুর্দশ দালাই লামা।
প্রফেসর থারম্যন বলেন, মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তাঁকে দালাই লামার দায়িত্ব নিতে হয়। ত্রিশের দশকেই চীনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। চিয়াংকাইশেকের কুয়োমিন্তাং পার্টি ও মাও যেদোংএর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ যুদ্ধ আরো বেগবান হয় এবং ১৯৪৯ সালে শেষ পর্যন্ত মাও জয়ী হয়। আর কাইশেক কেবল ফরমোসা দ্বীপ বা তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে থেকে যান। কিন্তু চীনের মূল ভূখণ্ডে মাও শুরু করে দেন শ্রেণী বিপ্লব। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের দ্বারা তৈরি হওয়া অভিজাত শ্রেণীদের হটিয়ে সর্বহারা বা প্রোলেটারিয়েটদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সারা দেশ জুড়ে তুলকালাম শুরু হয়। তিব্বতকে সামলানোর দায়িত্ব দেয়া হয় দাং শাওপিংকে। যিনি পরবর্তীতে মাওয়ের সমাজতন্ত্রকে একটু বদলে নিয়ে বর্তমান আধুনিক চীনের অগ্রযাত্রার গোড়াপত্তন করেন। এই দাং তিব্বতে কঠোর হাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা শুরু করেন। কৃষি ও পশুপালনভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় এমনিতেই খুব বড়সড় শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তারপরও দাং কিছুটা জোর করেই লাসার অভিজাত কিছু পরিবারকে হেনস্থা করেন। আর সেই সময়ে দালাই লামা ১৫ বছর বয়সে সমগ্র তিব্বতের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব নিয়ে সমাজতান্ত্রিক চীনের সাথে তিব্বতকে একীভূত করতে পূর্ব চীনে ঘুরে বেড়ান। এ সময়ে তিনি মাওসহ চৌ এনলাই, শি ঝোংশুনের (বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিনপিংএর পিতা) সাথে কাছ থেকে মেশার সুযোগ পান। এবং ১৯৫৯ পর্যন্ত তিনি চীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহরে ঘুরেন। কিন্তু তিব্বতের মধ্যেই অনেকগুলো দল চীনের কমিউনিস্ট দখলের বিপক্ষে লড়ে যাচ্ছিল। আর সেই সূত্র ধরে ১৯৫৯ সালে চীনের সামরিক বাহিনী গান্দেন ফোদরাং বা গেলুগ ধারার কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেয়। আর সেই সময়েই তেনজিন সিক্কিম হয়ে ভারতের ধর্মশালায় আশ্রয় নেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি তেনজিনকে আশ্রয় দিলেও তিব্বতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। আসলে অধিকাংশ দেশই দেয় নি। ফলে বিশ্বে তিব্বতের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন কোনটির দাবীই জোরালো হয়নি। উলটো সত্তরের দশকে তাইওয়ানের বদলে কমিউনিস্ট চীন পুরো বিশ্বে সত্যিকারের চীনের স্বীকৃতি পায়। ইউএসএ কোল্ড ওয়ারের সময়ে চীনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে তিব্বতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তেনজিন পৃথিবীর নানা প্রান্তে সফর করে বৌদ্ধ মতবাদ ও তিব্বতের দাবি নিয়ে বহু সম্মেলন ও সাক্ষাৎকার দেন। ফলে তিনি সারা বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।
আর দালাই লামার এই স্বপ্ন দেখার পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আছে ৪টি আশার কথা। ৪টি পর্যবেক্ষণঃ-
১। শান্তির বিস্তারঃ ১০০ বছর আগেও মানে ১৯০০ সালের দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্যকার ঘটনা। বড় বড় দেশগুলো কারো না কারো সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। শান্তির সময় ছিল শুধুমাত্র দুই যুদ্ধের মধ্যকার সময়। আর এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ শান্তির গুরুত্ব নিয়ে আরো সচেতন হয়েছে। অনর্থক যুদ্ধ-সংঘাতে জড়াচ্ছে না দেশগুলো। পুরোপুরি যুদ্ধ উবে না গেলেও একশ বছরের বিবেচনায় অবস্থার যে উন্নতি হয়েছে তা স্বীকার করে নিতেই হবে।
২। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টাঃ সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও মানুষ বিরাট বিরাট চিন্তাধারা বা মতবাদের উপর ভরসা করতো যে এগুলো তাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যা দূর করে দিবে। ধর্ম, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক পদ্ধতি - এসবের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সাধারণের সকল অসুবিধা হটিয়ে শান্তির পৃথিবী তৈরি করবে। কিন্তু এই একশ বছরে মানুষের এই ধারণা বদলেছে। এখন মানুষ অন্তত এইটুকু বুঝে যে, এসবের পরেও সবারই নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব আছে। এগুলোকে ভুলে গেলে হবে না। নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
৩। পরিবেশ নিয়ে সচেতনতাঃ ১৯০০ সালেও পৃথিবীর মানুষ পরিবেশ নিয়ে একদম সচেতন ছিল না। ময়লা-আবর্জনা বা শিল্প বর্জ্য যেখানে সেখানে তারা ফেলতো। তাদের ধারণা ছিল, পৃথিবী নিজ থেকেই নিজেকে পরিষ্কার করে নেবে। কিন্তু এখন মানুষ বুঝেছে, এত ব্যাপক হারে দূষণ চলতে থাকলে কেবল প্রকৃতির একার পুরোপুরি শুদ্ধিকরণ সম্ভব নয়। মানুষকেও সচেতন হতে হবে। যা তারা এখন আগের থেকে অনেক ভালভাবে করছেও।
৪। শিক্ষার গুরুত্বঃ ১০০ বছর আগে মানুষ ভাবতো, যেকোন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ দুঃখ-জরা, মৃত্যু বা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে তারা। নিত্য নতুন প্রযুক্তি আসবে এবং মানুষের একেকটি করে সমস্যা চলে যাবে। তাদের নিজেদের থেকে কিছু জানার বা করার দরকার নেই। এখন তা বদলে গেছে অনেকখানিই। তারা এখন শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল। ফলে উদারতা ও সংযমের ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ বেড়েছে।
এই চার নম্বর আশার ক্ষেত্রে হালকা দ্বিমত আছে আমার, বলা যায়। এই তুলনাটি খুব সম্ভবত ইন্টারনেট যুগের বিস্ফোরণের আগে করা হয়েছে। এখন মানুষ আরো বেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কোন জ্ঞানার্জন বা সহিষ্ণুতার দিকে মানুষের আগ্রহ হারাচ্ছে। নতুন কিছু শিখার আগ্রহ যেমন কমে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে, তেমনি সহনশীলতার দুয়ার ক্রমশ ছোট হচ্ছে। তবে অবশ্যই এটা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।
আমরাও আশাবাদী হতে চাই। সামনের সময় আরো শান্তির হবে, মানুষের মাঝে হিংসা-লোভের উপশম হবে, বৃথা হয়রানি থেকে মানুষ মুক্তি হবে, একজনের সাথে আরেকজন অর্থ, জাতি বা স্বার্থের বদলে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বাঁধনে যুক্ত হবে। আমাদের কৃত কাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যাতে সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিৎ। কেননা আমরা সেই সময়ে জীবিত থাকবো না - এই ধরণের চিন্তা খুবই সংকীর্ণমননের পরিচায়ক। আমাদের কুশলী জীবনযাপন করতে হবে।
এই যে এত বাক্যব্যয় করলাম, নানা পদের তথ্য-দর্শনের কচকচি কপচিয়েছি, এর থেকে মোটেও এটা প্রতীয়মান হয় না যে আমি এই বিষয়ে বিদ্বান বা পণ্ডিত কেউ। যৎসামান্য কিছু পড়েছি, ভিডিও দেখেছি। তা থেকে নিজের জন্য নোট নিতে নিতে ভাবলাম একটা মোটামুটি লেখা দাঁড় করানো যায়। অন্তত সংগ্রহে থাকবে। বেশিরভাগ জিনিসই উপযুক্ত উৎস থেকে নেয়া। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের মতো এতো পুরনো আর এরকম বিশাল একটা জিনিস নিয়ে সম্পূর্ণ জানাটা প্রায় অসম্ভব দু-আড়াই মাসের অল্প সময়ে। তার উপর এতো এতো শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে এই মতবাদ যে সকল ধারা সম্পর্কে একদম সঠিক ধারণা নেয়া বেশ কঠিন। ফলে, ভুলত্রুটি বা বেঠিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে এবং চোখে পড়লে অবশ্যই ধরিয়ে দেবেন। আর এতোবড় একটা কিছু নিয়ে অল্প কিছু লেখার যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছি তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।
ཨྃ མ ཎི པདྨེ ཧཱུྃ
ॐ मणि पद्मे हूँ


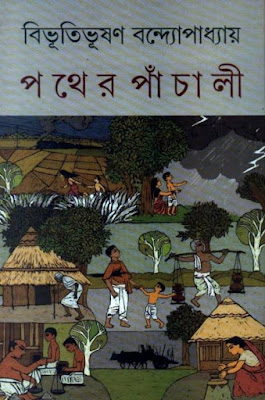
প্রায় পুরো লেখাটা পড়লাম, ফয়সাল ভাই। আরো কয়েকবার রিভাইস দেওয়া লাগবে। অসম্ভব ভালো লিখেছেন!
ReplyDeleteঅনেক ধন্যবাদ। কিছু পরিবর্তন বা পরিমার্জনের থাকলে অবশ্যই জানাবে।
Deleteআশিস নিরন্তর।
খুব ভাল লাগল। তথাগত আপনাকে ভাল রাখুন।
ReplyDelete